ম্যাকারেরে প্রাঙ্গণের স্বপ্নাবলি
নগুগি ওয়া থিয়ং’ও
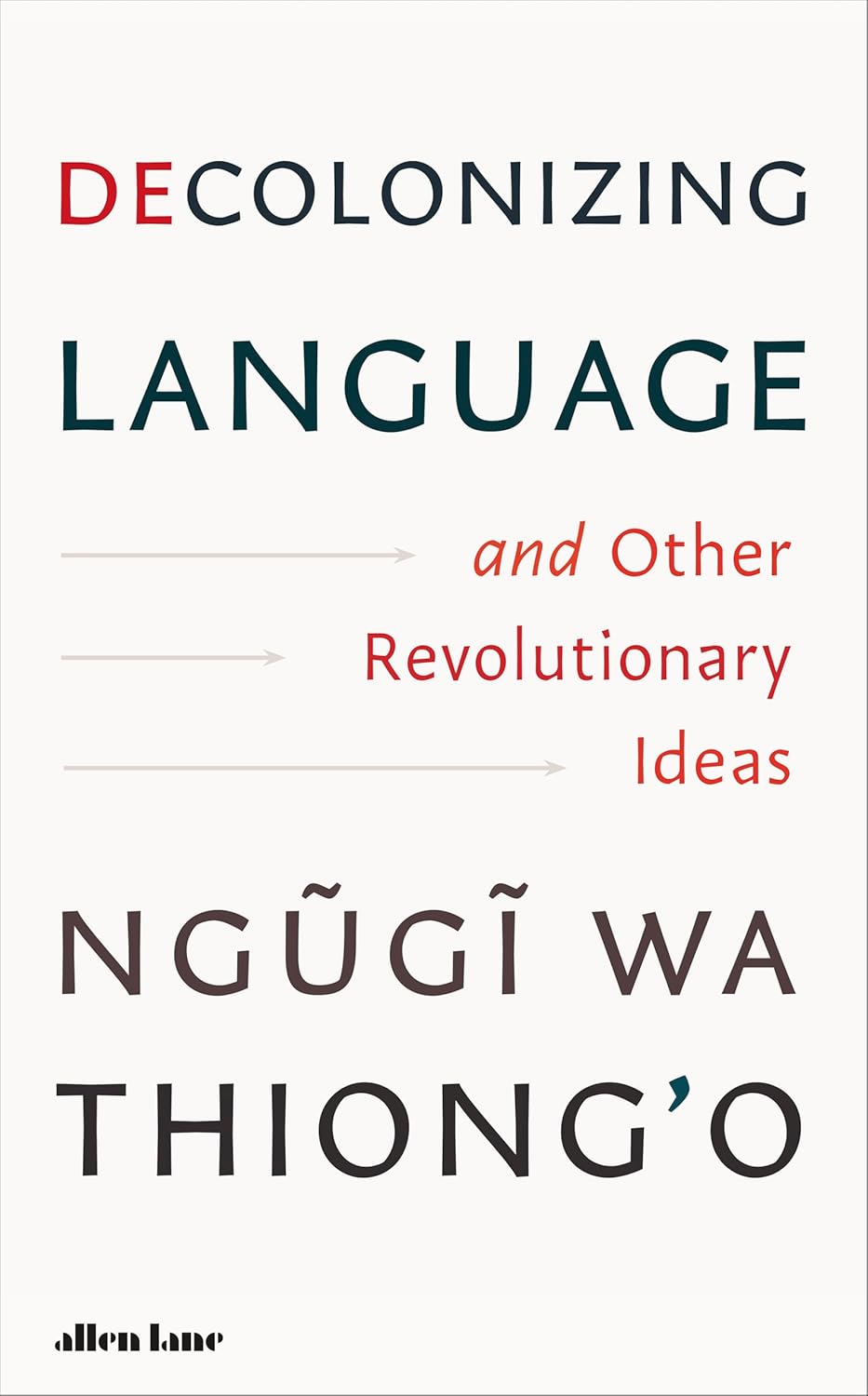
নগুগি ওয়া থিয়ং’ও (১৯৩৮-২০২৫) কেনিয়ার জগদ্বিখ্যাত উপনিবেশবাদ-বিরোধী বুদ্ধিজীবী। তিনি এ বছরের মে মাসে মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমান প্রবন্ধটি — ম্যাকারেরে ড্রিমস — তাঁর জীবদ্দশায় সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থে — ডিকলোনাইজিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড আদার রেভল্যুশনারি আইডিয়াস এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন দৈনিক নিউ এজ-এর সম্পাদক ও ইতিহাস-গবেষক নূরুল কবীর।
সেই ১৯৬১ সাল থেকে, বছরের পর বছর, আমরা একটি স্বপ্নের বাস্তবায়নকে উদ্যাপন করেছি, যে স্বপ্নের সফলতার জন্য দারুস সালাম, নাইরোবি আর কাম্পালার রাস্তায় রাস্তায় ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে লড়াই চলেছে। ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংসদ, তার ‘এক ব্যক্তি, এক ভোট’-ভিত্তিক অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ইতঃপূর্বেই ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছিল। ফলে, ম্যাকারেরের শিক্ষার্থীরা তীর্থের কাকের মতো এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিল। ম্যাকারেরে শিক্ষার্থী সংসদ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সমাজের জন্য যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা এখন তানজানিয়া, উগান্ডা ও কেনিয়ার সর্বত্র রাজনীতি-চর্চার স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হবে।
প্রথমে তানজানিয়া আর উগান্ডা স্বাধীনতা লাভ করেছিল। এরপর কেনিয়া যখন স্বাধীন হলো, আমরা সবাই আনন্দে কাম্পালার রাস্তায় নেমে এলাম — আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আমরা শিগগিরই একটা ‘পূর্ব আফ্রিকান ফেডারেশনের’ কল্পনা করতে শুরু করলাম। ইতঃপূর্বে কাম্পালায় অনুষ্ঠিত একটি যৌথ সমাবেশে জুলিয়াস নেরেরে, জোমো কেনিয়াত্তা ও মিল্টন ওবোতোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি আমাদের এই কল্পনাকে বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি দান করেছিল। সেই যৌথ সমাবেশে আমরা নেচে নেচে গেয়েছিলাম:
আমরা নেরেরেকে
স্বাধীনতার এক অভিযানে পাঠিয়েছিলাম।
কেনিয়া উগান্ডা তানজানিকা
আমরা একে অন্যের সহায়ক।
কালক্রমে এই গানে আমরা অন্য দুজন নেতার নাম যুক্ত করেছিলাম — কেনিয়াত্তা ও ওবোটু। কেন নয়? কাম্পালার ম্যাকারেরে পর্বতে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমরা তো বৃহত্তর পূর্ব আফ্রিকার মানুষ হিসেবেই জীবনযাপন করেছি — আঞ্চলিক পরিচয় নির্বিশেষে আমরা নেতৃত্ব নির্বাচন করেছি।
নেরেরে একসময় তিনটি স্বাধীন দেশের সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য, প্রয়োজনে, কেনিয়া ও উগান্ডার স্বাধীনতার জন্য এমনটি তানজানিকার স্বাধীনতা বিলম্বিত করারও আশ্বাস দিয়েছিলেন। বাস্তবে সেটা ঘটেনি। কিন্তু এক দশকব্যাপী রক্তাক্ত যুদ্ধ শেষে কেনিয়ার স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর, যে স্বপ্ন একসময় শুধু সংগীতের ভেতর মর্মরিত হতো, তা আজ বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আমরা যারা সেদিন কাম্পালার ম্যাকারেরেতে ছিলাম, তাদের জন্য এই অপূর্ব মুহূর্তটিকে মূর্তিমান করে তোলার লক্ষ্যেই যেন-বা কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই পঙ্ক্তিমালা:
সেই অপরূপ ভোর স্রেফ দেখতে পাওয়াই ছিল অপার আনন্দের,
আর অপূর্ব সেই প্রভাতে তরুণ থাকাটা ছিল এক স্বর্গীয় ব্যাপার।
ওয়ার্ডসওয়ার্থ আসলে ফরাসি বিপ্লব ও তার মধ্যে নিহিত সোনালি ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানিয়ে এই পঙ্ক্তিমালা রচনা করেছিলেন। আমাদের দিক থেকে তা ছিল — ‘পূর্ব আফ্রিকান ইউনিয়ন’ গড়ে ওঠা ও তার ভেতরে নিহিত ইতিবাচক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে স্বাগত জানানো।
পূর্ব আফ্রিকান হিসেবে এটি ছিল আমাদের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত — এমন একটি সময় যা আমাদের অনেক বড় স্বপ্ন দেখার সাহস জুগিয়েছে। এক জাদুকরী রূপান্তরের সময়। স্পষ্টতই এই জাদু আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমি ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে, একটি বসতিস্থাপনকারী শ্বেতাঙ্গ-রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক প্রজা হিসেবে, আর সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি বেরিয়ে আসি ১৯৬৪ সালে — একটি স্বাধীন কালো রিপাবলিকের নাগরিক হিসেবে। আর এই সময়কালে ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয় নিজের শরীর থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔপনিবেশিক উপাঙ্গটি খসিয়ে ফেলে ‘পূর্ব আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।
১৯৬৩ সালের ২৮ জুন সৃষ্ট পূর্ব আফ্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৭০ সালের পহেলা জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে বিলয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই বিলয়কে আমি বরং নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয় ও দারুস সালাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ঘটনা হিসেবে দেখতে পছন্দ করি, যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কালক্রমে পূর্ব আফ্রিকায় আরও অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করেছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে ধরনের পরিমাণগত, এমনকি গুণবাচক, পরিবর্তনই সাধিত হোক-না কেন, ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের ভেতর থেকে উঠে আসার কারণে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের ভেতর সে ঐতিহ্যের খানিকটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন ম্যাকারেরের প্রাক্তন স্নাতক। এদের একটি ‘ধারাবাহিকতা’ হলো, যা তাদের পরস্পরকে বিনিসুতার মালায় গেঁথে রেখেছে, নতুন ব্যবস্থায় তাদের প্রদত্ত স্নাতক ডিগ্রির সনদকে আর লন্ডন থেকে ন্যায্যতা জোগাড় করতে হয় না।
ম্যাকারেরের মতো মহৎ প্রতিষ্ঠানটির এই রূপান্তরের ঐতিহাসিক মুহূর্তকে উদ্যাপন করা আসলে একইসঙ্গে তার বিশাল অর্জনকেও সম্ভাব্য সকল উপায়ে স্মরণ করার শামিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির আফ্রিকার নানা অঞ্চল থেকে তো বটেই, এমনকি দুনিয়ার অন্যান্য জায়গা থেকেও, বহু কীর্তিমান স্নাতক তৈরি করেছে যাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীসহ অসংখ্য ডাক্তার, কৃষিবিদ, অধ্যাপক, কূটনীতিক, লেখক, সংগীতকার, শিল্পী ও ক্রীড়াবিদ।
আমি পরিচিত পৃথিবীর থেকে এমনসব দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছি, যেখানে চেনা-জানা মানুষের সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ, কিন্তু পরক্ষণেই সেখানে কোনো-না-কোনো ম্যাকারেরে-স্নাতকের দেখা মিলেছে। সেবার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লন্ডন হয়ে আমার নাইরোবি যাওয়ার পথে বিষয়টি আবারও প্রমাণিত হলো। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে বিনিদ্র রাত যাপনের ক্লান্তি নিয়ে আমি সবেমাত্র হিথ্রো বিমানবন্দরের ‘বিজনেস-ক্লাস লাউঞ্জে’ প্রবেশ করেছি। ঠিক তখনই ফলের সালাদ নিতে উদ্যত একজন কালো আফ্রিকানের ওপর আমার চোখ পড়ল এবং আমরা মাথা ঝুঁকিয়ে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানালাম। তার নাম ড. জোন্স ফিজে — জাতিসংঘের প্রাক্তন ইউনেস্কো প্রতিনিধি এবং পরে মুটিসা আই রয়েল ইনিভার্সিটি কাউন্সিলের একজন নির্বাচিত সদস্য। তিনি সেদিন লিসবনে অনুষ্ঠিত ‘রোটারি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন’ থেকে ফিরছিলেন, ফলে আমারই মতো একজন ‘ট্রানজিট-যাত্রী’ হিসেবে হিথ্রোর লাউঞ্জে রয়েছেন। আমার ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসার দু-বছর পর তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন এবং আমারই মতো তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থকোর্ট হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। তবে আমাদের মধ্যে অমিল ছিল আমাদের অর্জিত ডিগ্রির সনদ পরিচিতির ভেতর। আমার সনদে তখনও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মুদ্রিত ছিল, কিন্তু তাঁর সনদ ছিল সেই পরিচিতির বোঝা থেকে মুক্ত — পুরোপুরি ‘ইস্ট-আফ্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়’ নামাঙ্কিত।
ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ‘ম্যাকারেরে নিউজ লেটার’ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ম্যাকারেরে স্নাতকদের ঠিকুজি তালিকাবদ্ধ রাখত, আর তার প্রয়াত সম্পাদক মার্গারেট ম্যাকফার্সন বছরের পর বছর তা সুচারুভাবে সংরক্ষণ করেছেন। এই মহতী নারীর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আমরা একজন ‘ম্যাকারে ব্যক্তিত্ব’, একজন সম্পাদক এবং এমন একটি জ্ঞানভান্ডারের সংরক্ষককে হারিয়েছি, যেই জ্ঞানকাণ্ড আফ্রিকায়, এমনকি গোটা পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে, তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে — রেখে চলেছে এখনো। এটা সেই জ্ঞানকাণ্ড যা, ১৯২২ সালে ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে, পুরো এক শতাব্দীর স্বপ্ন থেকে বিকশিত হয়েছে।
ম্যাকারেরে ছিল নানা রাজনৈতিক স্বপ্নের এক পরিসর। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যেহেতু উগান্ডা, কেনিয়া, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, মালাগুয়ি এমনকি জিম্বাবুয়ে থেকে আগত শিক্ষার্থীদের তার অভিন্ন প্রাঙ্গণে সমবেত করেছিল, আমাদের সকলের চেতনাপ্রসূত সকল স্বপ্ন বিমুক্ত করার জন্য এটাই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত পীঠস্থান। এই স্বপ্ন শুধু একটি ‘পূর্ব আফ্রিকান ইউনিয়ন’ প্রতিষ্ঠার প্রতিই নিবেদিত ছিল না, বরং তা ছিল এমন একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ আফ্রিকা নির্মাণ করা যে, পশ্চিমের একটি উপাঙ্গ হিসেবে নয়, বরং তার ‘আপন সত্তার’ ভেতরে নিজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ন্যায্যতার প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর।
ম্যাকারেরে আমাদের সাহিত্যিক-স্বপ্নেরও লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল। আমি কেনিয়া থেকে ১৯৫৯ সালে যখন ম্যাকারেরেতে আসি, কেনিয়া তখন ঔপনিবেশিক শক্তির ঘোষিত ‘জরুরি অবস্থার’ অধীন — রাস্তায় প্রায়ই কালো মানুষের লাশ ও নির্যাতিত শরীর পড়ে থাকে। আমরা তখন নিজ দেশে, ফ্রাঞ্জ ফানোঁ যেমন বলেছেন, শ্বেতাঙ্গ বসতি-স্থাপনকারীদের শহরে উপনিবেশিত মানুষের উদ্বিগ্ন জীবনযাপন করি। উপনিবেশিত শহর মানেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নানা স্বপ্নের কবরস্থান। এ অবস্থায়, ম্যাকারেরে প্রাঙ্গণই আমাকে আমার কল্পনার বিহঙ্গের ডানা মেলার মুক্ত আকাশ জোগান দেয়। এখানেই, এই ম্যাকারেরে প্রাঙ্গণেই, অসংখ্য ছোটগল্পসহ আমি আমার প্রথম উপন্যাস দুটি — উইপ নট, চাইল্ড ও দ্য রিভার বিটুইন — রচনা করি। তা ছাড়া, উগান্ডার স্বাধীনতা উদ্যাপনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আমার নাটক, দ্য ব্ল্যাক হারমিট, রচিত হয়েছিল। ম্যাকারেরে আমার লেখক সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে।
আমি কেনিয়া থেকে ১৯৫৯ সালে যখন ম্যাকারেরেতে আসি, কেনিয়া তখন ঔপনিবেশিক শক্তির ঘোষিত ‘জরুরি অবস্থার’ অধীন — রাস্তায় প্রায়ই কালো মানুষের লাশ ও নির্যাতিত শরীর পড়ে থাকে। আমরা তখন নিজ দেশে, ফ্রাঞ্জ ফানোঁ যেমন বলেছেন, শ্বেতাঙ্গ বসতি-স্থাপনকারীদের শহরে উপনিবেশিত মানুষের উদ্বিগ্ন জীবনযাপন করি।
আমি একা নই। আমি ছিলাম বরং জন নাগেন্ডা, পিটার নাজারেথ, জনাথান কারিয়ারা, বাহাদুর তেজানি, ডেভিড রুবাদিরি, মিছেরে মুগু প্রমুখসহ একটি গ্রুপের অংশ, যাঁরা ইংরেজি বিভাগের ম্যাগাজিন পেনপয়েন্টে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। পূর্ব আফ্রিকায় আমার প্রজন্মের প্রায় সকল লেখকই ম্যাকারেরের সৃষ্টি।
পূর্ব আফ্রিকায় লেখক সৃষ্টি করা ছাড়াও, ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ সালের জুন মাসে আফ্রিকার ইংরেজি ভাষার লেখকদের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন আয়োজন করেছিল। নাইজেরিয়ার চিনুয়া আচেবে, ওলে সোয়াংকা, জে.পি. ব্লার্ক ও ক্রিস্টোফার ওকিগবো, দক্ষিণ আফ্রিকার লুইস কোসি, এসকিয়া ফালেনে, আর্থার মাইমানে ও ব্লোক মডিসানে সেই সম্মেলনে যোগদান করছিলেন। এদিকে জন নাগেন্ডা, জনাথান কারিয়ারা, রজত নিয়োগী আর আমি সেই মহামিলনে পূর্ব আফ্রিকাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম। তা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ল্যাংস্টন হিউজ ও ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে আর্থার ড্রেইটন যোগ দিয়ে এই সম্মেলনকে যথার্থই একটি নিখিল-আফ্রিকান রূপ দিয়েছিলেন। ইতঃপূর্বেও কালো লেখকদের একাধিক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তা কখনোই আফ্রিকায় আয়োজিত হয়নি। ১৯৫৬ সালে রোমে ও ১৯৫৯ সালে প্যারিসে আফ্রিকার লেখকদের সম্মেলন হয়েছে। আফ্রিকার মাটিতে কালো লেখকদের ওই মাপের কোনো সম্মেলন ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথমবারের মতো আয়োজন করে।
পূর্ব আফ্রিকায় লেখক সৃষ্টি করা ছাড়াও, ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ সালের জুন মাসে আফ্রিকার ইংরেজি ভাষার লেখকদের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন আয়োজন করেছিল। নাইজেরিয়ার চিনুয়া আচেবে, ওলে সোয়াংকা, জে.পি. ব্লার্ক ও ক্রিস্টোফার ওকিগবো, দক্ষিণ আফ্রিকার লুইস কোসি, এসকিয়া ফালেনে, আর্থার মাইমানে ও ব্লোক মডিসানে সেই সম্মেলনে যোগদান করছিলেন।
এই লেখকগণই কালক্রমে নিখিল আফ্রিকা বুদ্ধিবৃত্তিক মঞ্চের প্রায় কাছাকাছি একটি বস্তু আমাদের উপহার দেন: বই — অন্যকথায়, আফ্রিকান সাহিত্য। আচেবে যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন গোটা আফ্রিকা মহাদেশ তাঁর জন্য শোক পালন করে। আচেবের উপন্যাস থিংস ফল অ্যাপার্ট, যেটি সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেনিস ব্রুটাসের রচনার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়, আফ্রিকাজুড়ে পঠিত হয়। তা ছাড়া, অন্যান্য লেখকের রচনা, যেমন: ওকট বিটেক ও ওলে সোয়াংকার সাহিত্য, আর তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের লেখক টিট্সি ডাঙ্গারেম্বা, নগোজি আডিচি ও ডোরেন বেইঙ্গানা প্রমুখের রচনাও গোটা আফ্রিকার সাহিত্যকর্ম হিসেবেই মহাদেশটির সর্বত্র সমাদৃত হয়। ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয় বস্তুত পূর্ব আফ্রিকার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতীক ও পরিসর হিসেবে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু একইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি নিখিল আফ্রিকান সাহিত্যের আঁতুড়ঘর হিসেবেও ভূমিকা পালন করেছে।
এই সম্মেলনেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, আফ্রিকান, আফ্রিকান জাতি, আফ্রিকা মহাদেশীয়, এমনকি প্রবাসী আফ্রিকান হিসেবে পরিচিত আমরা আসলে কারা — আমাদের যথার্থ পরিচয় কী? উল্লেখ্য, ওই সম্মেলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ইংরেজি ভাষায় লিখতেন: আমাদের তাবৎ কল্পনার যাবতীয় ফসলের ন্যায্যতা লন্ডনের স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ইতঃপূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শরীরী অস্তিত্বের বিলোপ ঘটলেও, এই সম্মেলনের সাফল্যের মাধ্যমে আসলে ওই সাম্রাজ্যের অশরীরী অস্তিত্বের বিজয় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল।
এই সম্মেলনেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, আফ্রিকান, আফ্রিকান জাতি, আফ্রিকা মহাদেশীয়, এমনকি প্রবাসী আফ্রিকান হিসেবে পরিচিত আমরা আসলে কারা — আমাদের যথার্থ পরিচয় কী?
ঔপনিবেশিক শক্তির অশরীরী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় পরিসরে থাকে তার ভাষা। কেননা, ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার মনের ভাবনা প্রকাশ করে। এটা শুধু সৃজনশীল লেখালিখি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। লন্ডনের আধিপত্য থেকে আমাদের শিক্ষাবিষয়ক স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরও, [ইংরেজিকে] আমাদের জ্ঞানচর্চার ভাষা নির্বাচনের মাধ্যমে, আমাদের যাবতীয় জ্ঞানগত তৎপরতা ইউরোপীয় অশরীরী সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই সক্রিয় থেকে যায়।
আমরা যারা ওই জ্ঞানসম্ভারের উত্তরাধিকারী ও জিম্মাদার, তাদের আজ, অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পর, ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহের উপাঙ্গ হিসেবে জ্ঞানচর্চার ফলাফলগুলো মূল্যায়ন করার সময় এসেছে।
[ইংরেজিকে] আমাদের জ্ঞানচর্চার ভাষা নির্বাচনের মাধ্যমে, আমাদের যাবতীয় জ্ঞানগত তৎপরতা ইউরোপীয় অশরীরী সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই সক্রিয় থেকে যায়।
আমি অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছি যে, জ্ঞানচর্চার বিষয়টি — তা যে কোনো ধরনের জ্ঞানই হোক-না কেন — এমনকি ধারণার দিক থেকেও, কোনো নিরপেক্ষ তৎপরতা নয়। জ্ঞান যারই করায়ত্ত থাকুক-না কেন, তা ইতিহাস ও সংস্কৃতিসহ যাবতীয় সামাজিক বাস্তবতাকে বিচার-বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। মানচিত্র-নির্মাতারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত করেছে যে, আফ্রিকা মহাদেশটি আয়তনের দিক থেকে ইউরোপের চেয়ে ছোট। পশ্চিম গোলার্ধের অনেকে তাদের কথাবার্তায় প্রায়ই আফ্রিকা মহাদেশকে একটি একক দেশ হিসেবে উল্লেখ করে থাকে।
এই জ্ঞানকাণ্ড এমন একটি ধারণার সূত্রপাত করে, এবং তা জারি রাখতেও সাহায্য করে যে, মিশরসহ সাহারা মরুভূমির উত্তরের গোটা অঞ্চলটি ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর সাহারার দক্ষিণাঞ্চল হলো সত্যিকারের আফ্রিকা, যেখানে মানুষের নানা ‘ট্রাইব’ বা গোত্র নিরন্তর মারামারিতে নিয়োজিত থাকে। তবে জ্ঞানের কিছুটা আলোকায়নের ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গির খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সাহারার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের পরিচয় সংক্রান্ত নামকরণের পরিভাষা ও আফ্রিকার নানা জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে নানা ‘যুদ্ধমান গোত্রের’ মতো শব্দচয়ন পশ্চিমের জ্ঞানচর্চায় ও সাধারণ্যে এখনো বিদ্যমান রয়েছে।
কিছুদিন আগে আমার ক্যালিফোর্নিয়া-আরভিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রগতিশীল সহকর্মীর কাছ থেকে আমি একটি ই-মেইল বা বৈদ্যুতিন বার্তা পাই, যেখানে তিনি আমাকে ‘ট্রাইবের’ ধারণাটি পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত করার পরামর্শ দেন। তিনি, আর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত গবেষণায় আগ্রহী আরও কয়েকজন পণ্ডিত নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিলেন, কীভাবে সমকালীন ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণায় আর মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও আফ্রিকা বিষয়ক পাঠ্যক্রমে ‘ট্রাইব’ সংক্রান্ত ধারণাটিকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমার বৈদ্যুতিন বার্তার প্রেরক সহকর্মী যথার্থই স্বীকার করেছেন যে, ‘ট্রাইব’ একটি ঔপনিবেশিক শব্দ, আর ‘গ্লোবাল সাউথ’ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে ‘ট্রাইবের’ ধারণাটির সঙ্গে একটি জটিল ইতিহাস জড়িত রয়েছে; তবুও তিনি দাবি করেছেন যে, আমরা যেসব সমাজ সম্পর্কে গবেষণা করি, তাদের অধিকাংশের বেলায় না হলেও অনেকের বেলায় ‘ট্রাইব’ একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণা হিসেবে, এমনকি ওইসব সমাজের পরিচয়বাচক শব্দ হিসেবে, এখনো যথেষ্ট পরিমাণে প্রযোজ্য রয়েছে।
আবারও সেই [ইংরেজি] পাঁচ অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দ! আমি জানি, আমার সহকর্মীর পরামর্শের পেছনে সামান্যতম বদ-উদ্দেশ্যও ছিল না। কিন্তু তবুও এই পরামর্শ দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে যায়। কয়েক বছর আগে আমি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকার রাজনীতিতে ট্রাইব সংক্রান্ত কল্পকাহিনির ওপর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম, যেখানে আফ্রিকার ব্যাপারে মানুষের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে পণ্ডিত ও সাংবাদিকরা এই পাঁচ অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দটিকে কীভাবে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করেন, তা ব্যাখ্যা করেছিলাম।
আফ্রিকার মানুষের ওপর জবরদখল ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে উপনিবেশবাদীরাই ‘ক’ গোত্র বনাম ‘খ’ গোত্রের টেম্পলেট বা নমুনাটি তৈরি করে। অন্যকথায়, এই নমুনা তৈরির ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য ছিল, আচেবের উপন্যাস থিংস ফল অ্যাপার্টের জেলা প্রশাসক যেমন বর্ণনা করেছিল, নিম্নশ্রেণির নিগ্রো গোত্রগুলোকে ঠান্ডা করা। আফ্রিকার যে কোনো অঞ্চলের যে কোনো সংকট ব্যাখ্যা করার জন্য সাংবাদিকরা এই ‘ক’ গোত্র বনাম ‘খ’ গোত্রের টেম্পলেট ব্যবহার করে থাকে। যে কোনো সংকটের প্রধান চরিত্রগুলো কোন কোন সম্প্রদায়ভুক্ত — সাংবাদিকরা শুধু সেটুকু দেখেই মনে করে যে তাঁরা সমস্যাটিকে পরিষ্কারভাবে বুঝে ফেলেছেন। সমস্যাটি ‘ক’ ও ‘খ’ গোত্রের ভেতর ঐতিহ্যগত শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয় — স্রেফ গোত্রযুদ্ধ। অনেক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতও এমনকি এই অভিন্ন ‘নমুনাটি’ ব্যবহার করে থাকেন। সেক্ষেত্রে, অন্যদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য শুধু এই যে, তাঁদের বায়নাটি প্রচুর পাদটীকা আর অ্যারিস্টটল ও হবস থেকে গৃহীত নানা উদ্ধৃতির আবরণে ঢাকা থাকে।
আফ্রিকার নানা ঘটনাকে নিরন্তর ‘ট্রাইবের’ আলোকে বিচার করার ফলে আফ্রিকার বাস্তবতার পেছনে সক্রিয় আসল উপাদানগুলোর চিত্র বিকৃত হয়ে যায়। আইসল্যান্ডের আড়াই লাখ অধিবাসীকে একটি জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তবে এক কোটির ইবো জনগোষ্ঠীকে ‘ট্রাইব’ হিসেবে কেন? ডেনমার্কের ৪০ লাখ অধিবাসী একটি ‘জাতি’, তাহলে দুই কোটির জোরুবাস জনগোষ্ঠী একটি ‘ট্রাইব’ কেন?
আফ্রিকার নানা ঘটনাকে নিরন্তর ‘ট্রাইবের’ আলোকে বিচার করার ফলে আফ্রিকার বাস্তবতার পেছনে সক্রিয় আসল উপাদানগুলোর চিত্র বিকৃত হয়ে যায়। আইসল্যান্ডের আড়াই লাখ অধিবাসীকে একটি জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তবে এক কোটির ইবো জনগোষ্ঠীকে ‘ট্রাইব’ হিসেবে কেন? ডেনমার্কের ৪০ লাখ অধিবাসী একটি ‘জাতি’, তাহলে দুই কোটির জোরুবাস জনগোষ্ঠী একটি ‘ট্রাইব’ কেন? ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে পণ্ডিত ও সাংবাদিকরা যখন ‘জাতি’ শব্দটি ব্যবহার করেন না, তখনও তাঁরা অন্তত ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষেরা নিজেদের যেসব নামে পরিচয় দেন, তাঁদের কথা সেভাবেই উল্লেখ করে থাকেন। যেমন: তাঁরা ইংরেজ, জার্মান, ফরাসি, চীনা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর কথা বলেন। কিন্তু আফ্রিকার বেলায় অভিন্ন পণ্ডিত ও সাংবাদিকদের ‘ট্রাইব’ শব্দটিকে উপাঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করতেই হবে। যেমন: জোরুবাস ট্রাইব, জুলু ট্রাইব। কিংবা ইবো ট্রাইবভুক্ত অমুক, গিকুইয়ো ট্রাইবভুক্ত তমুক ইত্যাদি। একজন ইংরেজ যখন রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার জেতেন, তাঁকে যথার্থই একজন ‘ইংরেজ’ ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু আফ্রিকার কেউ যখন রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল জেতেন, তখন তাঁর বর্ণনার জন্য তাঁকে অমুক ট্রাইব বা তমুক ট্রাইবভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অন্যান্য মহাদেশে বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানকে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশের বেলায়, নানা দেশের প্রেসিডেন্টদের শুধু সেসব দেশের প্রেসিডেন্ট বলে পরিচয় দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া যায় না, তাঁর ট্রাইব-পরিচিতিও সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়। ব্যাপারটা অনেকটা এ রকম: [কেনিয়ার] গিকুইয়ো ট্রাইবভুক্ত ঔপন্যাসিক নগুগিকে তাঁরই ট্রাইবভুক্ত জোমা কেনিয়াত্তা জেলে পুরেছেন।
বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানকে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশের বেলায়, নানা দেশের প্রেসিডেন্টদের শুধু সেসব দেশের প্রেসিডেন্ট বলে পরিচয় দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া যায় না, তাঁর ট্রাইব-পরিচিতিও সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়।
সম্প্রতি রয়টার্সের একটি নিবন্ধে ‘ট্রাইবাল রক্ত’ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ট্রাইবাল রক্তের কী রং? ‘ট্রাইব’ শব্দটির ব্যাপক ঔপনিবেশিক ব্যবহারের কারণে এটি এতই কলঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে, শব্দটির আদি জ্ঞানেন্দ্রিক-বৈজ্ঞানিক অর্থ যা-ই থাকুক-না কেন, এখন এটি তার নিন্দনীয় ঔপনিবেশিক ছাতার নিচেই স্থান লাভ করেছে।
ট্রাইব শব্দটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক সূত্রে পরিণত হয়েছে। কোনো পাঠক এই শব্দটি দেখামাত্রই ধরে নেয় যে, সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি যা-ই করছে, তা তার সহজাত ‘ট্রাইবাল’ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই করছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি চর্চার প্রক্রিয়ায় শাসনপ্রণালি, গণতন্ত্র, সম্পত্তির মালিকানা, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, আঞ্চলিক উন্নয়ন ও দুর্নীতির মতো বাস্তব বিষয়গুলো বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে যায়। তখন মনে হয়, কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তি দুর্নীতিপরায়ণ কেবল এই জন্য যে, তার রক্তে কোনো বিশেষ ট্রাইবের সঙ্গে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কোনো জিন বা বংশাণুর অস্তিত্ব বিদ্যমান।
ফলে, আমার সহকর্মীর পাঠানো বৈদ্যুতিন বার্তাটির ব্যাপারে আমি দ্রুত ও সরাসরি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি: ট্রাইব শব্দটির পুনর্বাসন করার চেষ্টা তো দূরের কথা, আমাদের বরং উচিত শব্দটির ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। আমার সহকর্মী বলেছিলেন, তিনি মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় কাজ করেছেন এবং এই শব্দটি সেসব জায়গায় ব্যবহৃত হতে দেখেছেন। অন্যকথায়, আফ্রিকার মানুষেরাই এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। এ ব্যাপারে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, আফ্রিকার মানুষের এই শব্দটি ব্যবহার করার সোজা কারণ হলো, তারা নিজেরা একটি নেতিবাচক জিনিসকে আত্তীকরণ করে ফেলেছে। একটি অস্বাভাবিকতা স্বাভাবিকতায় পরিণত হয়েছে, তার ‘অস্বাভাবিকতা’ না হারিয়েই শব্দটি সমাজে স্বাভাবিকতা অর্জন করেছে। কিন্তু আমার সহকর্মীর ব্যবহৃত ‘ক্বাবিলা’ শব্দটি, আরবি ভাষায় যা ট্রাইবেরই সমার্থক, আমাকে ভাবিয়ে তোলে।
আরবি ‘ক্বাবিলা’ শব্দটি কিসোয়াহিলি ভাষায় ‘কাবিলা’ আর গিকুইয়ো ভাষায় ‘কাবিরা’ হয়ে যায়। কিন্তু এই শব্দগুলো, ইংরেজিতে যেমন, একই গোত্রভুক্ত হলেও, তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে। এগুলো যতটা-না উন্নয়ন ও আধুনিকতা সংশ্লিষ্ট পার্থক্য-নির্দেশক শব্দ, তার চেয়ে বেশি কোনো নির্দিষ্ট বাস্তবতার বর্ণনাবাচক শব্দাবলি। আমার নিজের [গিকুইয়ো] ভাষায়, ‘রুরিরি’ বলতে অভিন্ন ভাষা, ভূমি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন কোনো সম্প্রদায়কে বোঝায়, যার মধ্যে নেতিবাচকতার কিছু নেই। কিন্তু ইউরোপীয় ভাষাসমূহে, বিশেষত ইংরেজি ভাষায়, ট্রাইব বা ট্রাইব্সম্যান শব্দের ভেতর নেতিবাচকতা বিদ্যমান। ইংরেজি ‘ট্রাইব’ শব্দটি, তার ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্যের কারণে, বহিরাগতের পরিভাষা হিসেবেই বিবেচিত হয়।
ইউরোপীয়দের আফ্রিকা সংক্রান্ত গবেষণায় প্রচলিত নানা পরিভাষা ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিকদের হাতেই নির্মিত হয়েছে। স্থানীয় নানা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ইউরোপীয় বহিরাগতদের গবেষণা কার্যক্রম ওই বহিরাগতদের প্রয়োজনেই পরিচালিত হয়েছে। বহিরাগত ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিকগণ উপনিবেশিত নানা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করেছেন এবং সেসব তথ্য নিজেদের ভাষার ভেতর সঞ্চয় করেছেন, আর সে জন্য আমরা তাদের দোষারোপ করতে পারি না।
আমরা বরং যা বলতে পারি তা হলো, আফ্রিকার নানা বিষয় সম্পর্কে আমাদের তাবৎ জ্ঞানের নানা ধারা, আসলে, ইউরোপীয় বহিরাগতদের দৃষ্টিতে আফ্রিকাকে দেখার ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের ভেতর প্রোথিত। ইউরোপীয় বহিরাগতরা তাদের স্থানীয় সহকারীদের মাধ্যমে স্থানীয় নানা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন এবং সেসবের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলো, ইউরোপীয় ভাষাসমূহের ভেতর প্রবেশযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারের জন্য, ইউরোপীয় নানা ভাষায় মজুত করেছেন। অন্যকথায়, আমরা এখনো আফ্রিকা সম্পর্কে নানা বুদ্ধিবৃত্তিক উপাদান সংগ্রহ করে ইউরোপীয় ভাষার জাদুঘর আর মহাফেজখানায় জমা করি। এ অবস্থায়, নিজেদের সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ফলাফল জানতে আফ্রিকার মানুষকে নানা ইউরোপীয় ভাষার ভেতর প্রবেশ করার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। স্পষ্টতই, আফ্রিকা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রধানত ইংরেজি ভাষা ও শব্দকোষের মধ্য দিয়ে পরিস্রাবিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছায়। তাহলে, ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের ন্যায্যতা আহরণের প্রয়াস ত্যাগ করার এটাই কি উপযুক্ত সময় নয়, ঠিক যেভাবে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ম্যাকারেরে তার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে লন্ডনের কাছ থেকে ন্যায্যতা আহরণের প্রক্রিয়া বন্ধ করেছে?
নিজেদের সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ফলাফল জানতে আফ্রিকার মানুষকে নানা ইউরোপীয় ভাষার ভেতর প্রবেশ করার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। স্পষ্টতই, আফ্রিকা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রধানত ইংরেজি ভাষা ও শব্দকোষের মধ্য দিয়ে পরিস্রাবিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছায়। তাহলে, ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের ন্যায্যতা আহরণের প্রয়াস ত্যাগ করার এটাই কি উপযুক্ত সময় নয়
যখন ম্যাকারেরে চারুকলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মূর্তি বা প্রতিমা গড়ার জন্য লন্ডন থেকে কাদামাটি আমদানি করত। ইউরোপীয় মাটি ছাড়া যেন-বা ভালো শিল্পকর্ম হতে পারে না। কিন্তু যখন এলিমো নাউ, স্যাম নিরো ও গ্রেগরি মালোবার মতো শিল্পী ললিতকলার দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন, তাঁরা বললেন, ‘শিশুদের আঁকতে দাও। তাদের ভাস্কর্য বানাতে দাও। কলাপাতাসহ তাদের চারপাশে যা কিছু উপকরণ আছে, তা দিয়েই শিশুরা শিল্পচর্চা করুক।’ এভাবেই পূর্ব আফ্রিকায় ললিতকলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল।
একসময় যেভাবে বলা হয়েছিল যে, উগান্ডার মাটি ভালো শিল্পকর্মের জন্য উপযুক্ত নয় — ঠিক সেভাবেই অনেকে বলে থাকেন যে, সামাজিক চিন্তার নানা জটিল ব্যাখা-বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য আফ্রিকার ভাষাসমূহের নেই — গরিব আফ্রিকাবাসীর মতো তাদের ভাষাও দারিদ্র্য-জর্জরিত। পরিহাসের বিষয় হলো, একসময় আধিপত্যশীল ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষার স্বর্ণযুগে ইংরেজি ও ফরাসিকেও এই অভিন্ন অভিযোগ মোকাবিলা করে অগ্রসর হতে হয়েছিল — তখন বলা হতো যে, দর্শন ও বিজ্ঞান-চিন্তা ধারণ করার মতো পর্যাপ্ত ঋজুতা এই ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার মধ্যে অনুপস্থিত। কিন্তু আপন আপন ভাষার প্রতি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয় ও তাদের বুদ্ধিজীবীদের যথার্থ অঙ্গীকার এবং আপন আপন পরিসরে নিজস্ব ভাষার পর্যাপ্ত ব্যবহারের মাধ্যমে তৎকালে প্রচলিত এই নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তন ঘটে। আফ্রিকার বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রসমূহের দিক থেকেও আফ্রিকার ভাষাসমূহের প্রতি অনুরূপ অঙ্গীকার প্রয়োজন। পাশাপাশি, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, জ্ঞানেন্দ্রিক শব্দকোষের ওপর কোনো ভাষারই সহজাত একাধিপত্য থাকার কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া, চেইথ আনটা দিয়প যেমন যুক্তি প্রদর্শন করেন, প্রতিটি ভাষাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক পরিভাষা তৈরি করতে সক্ষম।
একসময় যেভাবে বলা হয়েছিল যে, উগান্ডার মাটি ভালো শিল্পকর্মের জন্য উপযুক্ত নয় — ঠিক সেভাবেই অনেকে বলে থাকেন যে, সামাজিক চিন্তার নানা জটিল ব্যাখা-বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য আফ্রিকার ভাষাসমূহের নেই — গরিব আফ্রিকাবাসীর মতো তাদের ভাষাও দারিদ্র্য-জর্জরিত।
ছিদ্রান্বেষী লোকেরা অবশ্য জোর গলায় বলতে থাকবে, আফ্রিকার কোনো ভাষাই লিখিত আকারের বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ৪০ লাখ নাগরিক অধ্যুষিত ডেনমার্ক যদি ডেনিশ ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকাদি দিয়ে তাঁদের গ্রন্থাগার ও বইয়ের দোকানগুলো ভরে রাখতে পারে, তাহলে এক কোটি মানুষের ইবো জনগোষ্ঠী কেন তা পারবে না? মাত্র আড়াই লাখ মানুষ অধ্যুষিত আইসল্যান্ড তো ইউরোপে উচ্চমাত্রার বুদ্ধিবৃত্তিক উৎপাদন বিকশিত করে চলেছে। আড়াই লাখ মানুষ যা করতে পারে, ১০ লাখ মানুষ নিশ্চয় তা করতে পারে। আমরা আজও গ্রিক ও ল্যাটিন বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের কথা বলি, কিন্তু ভুলে যাই যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে পরস্পর সম্পর্কিত নগরগুলোর মধ্যেই সেই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বিকশিত হয়েছিল। ইতালির বহুলপ্রশংসিত নবজাগরণ এবং সমসাময়িক কালের শিল্পকলা, স্থাপত্য ও জ্ঞানের বিকাশে সেই জাগরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমৃদ্ধ অবদানের ক্ষেত্রে রোম, ফ্লোরেন্স, মানটুয়া, ভেনিস ও জেনোয়া নগরীর বিরাট অবদান ছিল। এসব নগর-রাষ্ট্র, ছোট ছোট রাজ্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের নানা স্থানীয় ভাষায় অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তিক কীর্তিসমূহ, অনুরূপ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে, অন্য যে কোনো ভাষার পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব।
প্রশ্ন হলো: আফ্রিকার জ্ঞানচর্চায় ইউরোপীয় ভাষাসমূহের স্থান কোথায় হওয়া উচিত? যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তারা আমাদের ভূমি দখল করতে এসে আমাদের জীবনই দখল করে ফেলেছে, সে প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা যেভাবেই যা চিন্তা করি-না কেন, বাস্তবতা হলো এই যে, ইউরোপীয় ভাষাসমূহ — বিশেষত ইংরেজি, ফরাসি ও পর্তুগিজ — আফ্রিকার সবচেয়ে মহৎ সাধারণ ও সাহিত্যচিন্তার এক বিশাল অংশকে ধারণ করে চলেছে। এই ভাষাগুলো আফ্রিকার বুদ্ধিবৃত্তিক উৎপাদনের বিরাট ভান্ডার। এই ভাষাগুলো সমকালীন বৈশ্বিক সংস্কৃতিতে আফ্রিকার দৃশ্যমান উপস্থিতিকে সমর্থ করেছে। এই ভাষাগুলো জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কোনো সমাবেশে পরস্পরের ভেতর কথোপকথন সম্ভব করে তোলে। তবে, আমাদের সবাইকে এই ভাষাগুলো শিখতে হয়েছিল বলেই আমাদের এখন এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। এই ভাষাগুলোর সহজাত কোনো বৈশ্বিক বা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য নেই। এই ভাষাগুলো নানা কারণে ক্ষমতার ভাষা হয়ে উঠেছে।
এই ‘সমর্থ করার’ ধারণাটিই অতএব আমাদের বলে দেয়, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষাকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করব। আমাদের উচিত আমাদের বিদ্বৎসমাজ ও তাঁদের সৃষ্টিসমূহকে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার ভান্ডার থেকে অপসারণ করার সুযোগ না দিয়ে বরং আফ্রিকার ভাষাগুলোর ভেতর সংলাপ পরিচালনা ও বৈশ্বিক সমাজে আফ্রিকার ভাষাসমূহের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধির কাজে এই ইউরোপীয় ভাষা দুটিকে ব্যবহার করা। ইংরেজি ও ফরাসিকে আফ্রিকার ভাষাগুলোকে ‘সমর্থ করার’ কাজে ব্যবহার করুন, ‘অসমর্থ করার’ জন্য নয়।
আফ্রিকার বুদ্ধিজীবী হিসেবে, আমরা আমাদের নিজভূমে বহিরাগতের মতো আচরণ করতে পারি না। মাটি চাপাপড়া আফ্রিকার সামষ্টিক স্মৃতির পলির সঙ্গে আমাদের পুনঃসংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে আফ্রিকার ব্যাপকতর সম্পর্ক তৈরিতে সেই সামষ্টিক স্মৃতিকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীরা তাদের আপন আপন ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিবাচক বিকাশের জন্য যা যা করেছেন, আফ্রিকার বুদ্ধিজীবীদেরও নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য তা তা করতে হবে। এ অবস্থায়, বিশ্বায়নের বর্তমান যুগে, আমাদের বিদ্বৎজনদের কর্তব্য হলো, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ভেতর কার্যকর পারস্পরিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার উপায় অন্বেষণ করা। আপন আপন মাতৃভাষায় লেখালিখি করা অবশ্যই একটি উপায়, কিন্তু এরকম নানা ভাষায় লিখিত বুদ্ধিবৃত্তিক রচনার পারস্পরিক অনুবাদের মাধ্যমে আফ্রিকার ভাষাগুলোর ভেতর সংলাপ পরিচালনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
ভাষার ভেতরকার এই মিথস্ক্রিয়া সাধারণভাবে আফ্রিকার ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষমতায়ন ঘটাতে বাধ্য — প্রকারান্তরে যা আবার আফ্রিকার বর্ধিত আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে সক্রিয় থেকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে অধিকতর সমতাভিত্তিক লেনদেন প্রতিষ্ঠায় আফ্রিকাকে প্রণোদনা জুগিয়ে যাবে।
আপনি যদি নিজের মাতৃভাষা ছাড়া, জগতের অন্য সকল ভাষাও রপ্ত করে থাকেন, তাহলে আপনি আসলে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি রয়েছেন। অন্যদিকে, মাতৃভাষা যদি আপনার রপ্ত থাকে, আর তার সাথে যদি জগতের অন্যান্য ভাষার শক্তি যুক্ত করেন, তাহলে আপনার ক্ষমতায়ন ঘটেছে। আমাদের সামনে দুটি পথই খোলা আছে — বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বের ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতায়নের পথ। আমি অবশ্যই আশা করি যে, আমরা ক্ষমতায়নের পথকেই বেছে নেব।
আপনি যদি নিজের মাতৃভাষা ছাড়া, জগতের অন্য সকল ভাষাও রপ্ত করে থাকেন, তাহলে আপনি আসলে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি রয়েছেন। অন্যদিকে, মাতৃভাষা যদি আপনার রপ্ত থাকে, আর তার সাথে যদি জগতের অন্যান্য ভাষার শক্তি যুক্ত করেন, তাহলে আপনার ক্ষমতায়ন ঘটেছে।
কিন্তু বুদ্ধিজীবী বা বিদ্বৎজনরা একা এই দায়িত্ব নিষ্পন্ন করতে পারেন না। প্রকাশকদের সাহায্য প্রয়োজন। আমরা সকলেই জানি, একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করে, তার ওপর অন্তত চোখ বোলাতে আগ্রহী একজন প্রকাশকের অভাবে, সেই পাণ্ডুলিপি আলমারিবদ্ধ করে রাখা কি পরিমাণ হতাশাজনক অভিজ্ঞতা। আবার বুদ্ধিজীবী ও প্রকাশক একত্রিত হলেই চলে না, সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সরকার-প্রণীত আলোকিত ভাষানীতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আফ্রিকার সরকারগুলো আফ্রিকার বুদ্ধিজীবিতা হননের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এ ব্যাপারে [সাম্রাজ্যবাদী] বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের কতটা ভূমিকা আছে জানি না, কিন্তু আফ্রিকার সরকারগুলো আফ্রিকার ভাষাসমূহের সাথে বৈমাত্রেয় আচরণ করে চলেছে। আফ্রিকার ভাষাগুলোর শক্তিমত্তা বৃদ্ধির জন্য সরকারগুলো কোনো সম্পদ বরাদ্দ করে না, আর যেখানে তারা ভাষাগুলোকে সরাসরি গলাটিপে হত্যা করে না, সেখানে তাদের অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এই পথ কোমে নক্রুমার পথ থেকে অনেক আলাদা, যিনি ১৯৫৭ সালে ঘানার স্বাধীনতা অর্জনের পর রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে ‘আফ্রিকার ভাষাসমূহের ব্যুরো’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই পথ জুলিয়াস নেরেরের পথ থেকেও আলাদা, যিনি যথাযথ সরকারি নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে কিসোয়াহিলি ভাষার উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন এবং নিজে কিসোয়াহিলি ভাষায় শেক্সপিয়র অনুবাদ করেছিলেন। আফ্রিকার অপরাপর ভাষার প্রতি নেরেরের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল ছিল, তথাপি কিসোয়াহিলি ভাষাকে তিনি প্রয়োজনীয় ক্ষমতার ভিত জুগিয়েছিলেন। একসময় ম্যাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, নেরেরে পূর্ব আফ্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও একমাত্র আচার্যও ছিলেন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ভেতর একতা প্রতিষ্ঠার এই দুই অবিচল প্রবক্তা, (পরিত্রাণকর্তা) নক্রুমা ও (শিক্ষাদাতা) নেরেরে, আফ্রিকার ভাষাসমূহের তরফে ইতিবাচক নীতি প্রণয়নেরও শীর্ষস্থানীয় পক্ষপাতী ছিলেন। আফ্রিকার প্রতিটি দেশের উচিত একটি ‘আফ্রিকার ভাষাসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যুরো’ প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা, যে ব্যুরোর কাজ হবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে আফ্রিকার ভাষাসমূহের উন্নয়ন ও পারস্পরিক সম্পর্ক তদারকি করা।
এই পথ কোমে নক্রুমার পথ থেকে অনেক আলাদা, যিনি ১৯৫৭ সালে ঘানার স্বাধীনতা অর্জনের পর রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে ‘আফ্রিকার ভাষাসমূহের ব্যুরো’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই পথ জুলিয়াস নেরেরের পথ থেকেও আলাদা, যিনি যথাযথ সরকারি নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে কিসোয়াহিলি ভাষার উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন এবং নিজে কিসোয়াহিলি ভাষায় শেক্সপিয়র অনুবাদ করেছিলেন।
সুনির্দিষ্টভাবে পূর্ব আফ্রিকার ভাষানীতি প্রশ্নে আমার তিনটি প্রস্তাব: প্রতিটি দেশের মাতৃভাষার ভিতকে শক্তিমান করা, কিসোয়াহিলিকে সাধারণ ভাষা হিসেবে যুক্ত করা ও ইংরেজি ভাষার ভান্ডারটিকে অক্ষুণ্ন রাখা। পুস্তক প্রকাশনার প্রশ্নে আমি বলব, এই তিনটি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির পারস্পরিক অনুবাদ এবং অবশ্যই, আফ্রিকার নানা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির পারস্পরিক অনুবাদ, সামগ্রিকভাবে আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিজীবীরা ম্যাকারেরের স্বপ্নগুলো আরও সম্প্রসারিত করুক ও জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করুক। আফ্রিকা তার অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির নতুন নতুন ক্ষেত্র উদ্বোধন করুক। আফ্রিকা একটি নতুন, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, মানবজাতির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নবজাগরণের সামনের সারিতে অবস্থান গ্রহণ করুক। মানুষের ‘নতুন সত্তার’ বিকাশ প্রক্রিয়াটি আমাদের দিয়েই শুরু হোক। তাহলেই, লাখ লাখ শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্নের সঙ্গে আমাদের স্বপ্নগুলো একীভূত হবে।
