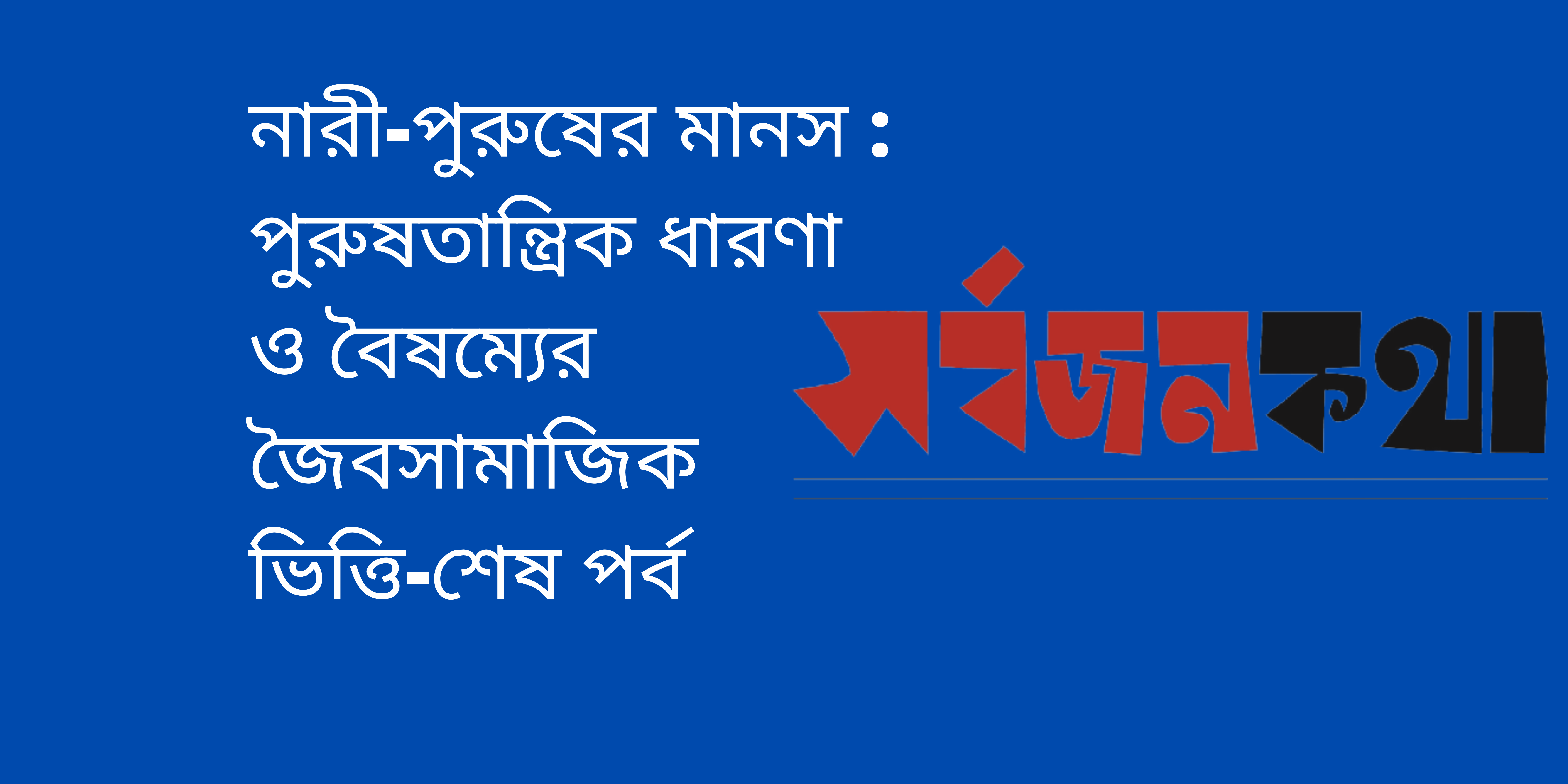নারী-পুরুষের মানস : পুরুষতান্ত্রিক ধারণা ও বৈষম্যের জৈবসামাজিক ভিত্তি-শেষ পর্ব
পুরুষতান্ত্রিক খাঁচার পাখি-নারীর মন
মনিরুল ইসলাম
“বশ্যতা নারীর প্রকৃতি বা নিয়তি কোনোটাই নয়। তারপরও পিতৃতন্ত্র, অন্যান্য সামাজিক কর্তৃত্বমূলক কাঠামোর মতো নিজেকে চিরস্থায়ী করার নানা কায়দা কানুন তৈরি করতে থাকে, এর অন্যতম হচ্ছে নারীকে বশে রাখা। মেয়েলিপনাকে উপস্থিত করা হয় কাক্সিক্ষত টাইপ হিসেবে, (নারীর) আনুগত্যকে চিত্রিত করা হতে থাকে তুষ্টি ও শক্তির উৎস হিসেবে এবং বারবার তুলে ধরা হয় নারী স্বাধীনতার বিপদসমূহকে। …সাধারণত একজন পুরুষের কাছেই এই বশ্যতা, কিন্তু এর শুরুটা হয় সমাজের রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য দিয়ে।”১১০
-ম্যানন গার্সিয়া
We Are Not Born Submissive
“গ্রীকদের সময় থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত নারীর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগগুলোর মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত এত মিল কেন তা আমরা এখন বুঝতে পারছি। বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও নারীর অবস্থা রয়ে গেছে একই রকম এবং এই অবস্থাই নির্ধারণ করে যাকে বলা হয় নারীর ‘চরিত্র : …এসবের (মানসিক বৈশিষ্ট্য) মধ্যে সত্যের উপাদান আছে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে (নারীর) যেসব বিচিত্র আচরণের কথা বলা হচ্ছে সেগুলো নারীর মধ্যে হরমোন দ্বারা পরিচালিত হয় না কিংবা নারী-মস্তিষ্কের সংগঠনে তা পূর্বনির্ধারিত নয়: পরিস্থিতির আদলেই এগুলো এই আকারে গড়ে ওঠে।”১১১
-সিমোন দ্য বুভোয়া The Second Sex
‘দুই পাখি’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে খাঁচার পাখির ছবি এঁকেছেন সে উড়তে ভয় পায়, মুক্তি চায় না, খাঁচাই তার কাছে পরিপাটি শান্তির আশ্রয় যেখানে নিরালায় থাকতেই তার ‘সুখ’। সীমাহীন আকাশ বা বনের মুক্ত-প্রান্তরে উড়ে বেড়ানোর আনন্দ তাকে টানে না। মুক্ত প্রান্তরের রোমাঞ্চ সে চায় না, নিরিবিলি ঘরের কোণে বসার ঠাঁই পেলেই সে ধন্য। বনের স্বতঃস্ফূর্ত সুর ও বাণীর বৈচিত্র তাকে স্পর্শ করে না তাই সে শুধু শেখানো বুলি আওড়ে চলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর মনের যে প্রকাশিত রূপ আমরা দেখতে পাই সেটা তার জন্মগত বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নয়। পুরুষতান্ত্রিক বাস্তবতাও এক নির্মম খাঁচা যেখানে আবদ্ধ নারীর মন ওই খাঁচার পাখির মতই বদলে যায়। খাঁচার পাখির মতো নারীর মধ্যেও ভীতু, আপোষকামী, আত্মবিশ্বাসহীন, সাবধানী, সুযোগ-সন্ধানী ও নতজানু এক সত্তা গড়ে ওঠে। এই বাস্তবতার মধ্যে একদিকে রয়েছে বন্দীত্ব, বৈষম্য, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও কঠোর অনুশাসন যার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে নারীর মন হয়ে ওঠে বাধ্য, অনুগত, আতঙ্কগ্রস্ত, নরম ও নতজানু। অন্যদিকে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ, মূল্যবোধ, মূল্যায়ণ, স্বীকৃতি ইত্যাদি যা নারীদের পুরুষতান্ত্রিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে উৎসাহিত করে। ফলে তারা সচেতন বা অবচেতনভাবে এই মানদণ্ডে ‘নারীসুলভ’হয়ে ওঠে। নারী যত কঠিন পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসনের মধ্যে বড় হয়, তার মধ্যে কথিত ‘নারীসুলভ’মানসিকতা ও আচরণের প্রবণতা তত গভীরভাবে প্রোথিত হয়। এ ধরণের একটি সমাজে ব্যাপক অধিকাংশ নারীর মধ্যে এ ধরণের প্রবণতার উপস্থিতির ফলে আপাতদৃষ্টিতে একে সার্বজনীন বলেও মনে হয়। নারীর এ ধরণের আচরণ এ সমাজে ক্ষমতাবান লিঙ্গ হিসেবে পুরুষকে সন্তুষ্ট করে কারণ এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে নারী তার অধস্তন অবস্থা মেনে নিয়েছে। অন্য দিকে নারী যখন অপেক্ষাকৃত মুক্ত পরিবেশে বড় হতে পারে কিংবা পুরুষতান্ত্রিক ধারণার প্রভাব কাটিয়ে কিছুটা মুক্তভাবে ভাবতে পারে তাদের মধ্যে ‘নারীসুলভ’মানসিকতা ও আচরণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে।
আমাদের সমাজে প্রচলিত ও আধিপত্যকারী ধারণা হল প্রকৃতিগত ভাবেই নারী ও পুরুষের মানসিকতা ও আচরণের ক্ষেত্রে বড় ধরণের পার্থক্য রয়েছে যা তাদের জৈবিক পার্থক্যের কারণে গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে ‘নারীসুলভ’বা ‘পুরুষালী’আচরণ ও মানসিকতা বলতে যা বোঝানো হয় তা তাদের জৈবিক যৌনতাকে নির্দেশ করে না। এগুলো মূলত লিঙ্গীয় ধারণা যা কেবল জৈবিক যৌনতার উপর নির্ভর করে না বরং সামাজিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়। আচরণ, অনুভূতি, ভাবনা, ফ্যান্টাসি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা আছে কিন্তু তা গড়ে ওঠে জৈবিক ও সামাজিক বাস্তবতার মিথষ্ক্রিয়ায়। পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর আদলেই গড়ে ওঠে ‘নারীসুলভ’ও ‘পুরুষালী’মনোভাব সম্পর্কে এ সমাজে প্রচলিত ধারণাগুলো। সমাজের ব্যাপক অধিকাংশ নারী ও পুরুষের মানসিকতা ও আচরণ এ ধরণেরই বা এর কাছাকাছি রূপে গড়ে ওঠে যা সে এ সমাজে বেড়ে ওঠার সময়ই শেখে। এখানে ‘নারীসুলভ’মানসিকতা বলতে যেমন ভীতু, সংকীর্ণ, আপোষকামী, আত্মবিশ্বাসহীন, সাবধানী, সুযোগ-সন্ধানী ও নতজানু মানসিকতাকে বোঝানো হয় তেমনি পুরুষালী মানসিকতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কঠোরতা, নির্বিকারত্ব, স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাব-ভঙ্গী, আবেগ ও সংবেদনশীলতা-বর্জিত মনোভাব, সম্পর্কিত বা অন্তরঙ্গ হবার প্রবণতার অভাব ইত্যাদি। এই জেন্ডার নির্দিষ্ট আচরণগুলি পুরুষতান্ত্রিক বাস্তবতার চাপে কিংবা এই বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা থেকেই নারীপুরুষের মধ্যে স্থায়ী হয়। নারীপুরুষের এই প্রকাশিত আচরণের আপাত পর্যবেক্ষণ থেকেই গড়ে ওঠে তাদের মানস সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাগুলো। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মূলধারা এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রকৃতিগত বা জৈবিক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কারণ লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক এই সমাজ নারী ও পুরুষের কাছে যে মনোভাব ও আচরণ আশা করে তাকে ‘জৈবিক’প্রবণতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে এগুলোকে ‘স্বাভাবিক’, ‘পরিবর্তনযোগ্য নয়’কিংবা ‘গ্রহণযোগ্য’বলে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়।
মন আমাদের বোধের অংশ যা গঠিত হয় চেতনা, কল্পনা, উপলব্ধি, চিন্তা, বিচারশক্তি, ভাষা, স্মৃতি ইত্যাদির সমন্বয়ে। এগুলোকে ধারণ করে মস্তিষ্কের সেই অংশ যেখানে চিন্তা ও চেতনা ক্রিয়াশীল থাকে এবং এটি আমাদের কল্পনাশক্তি, অভিরুচি, আবেগ ও অনুভূতিকেও ধারণ করে। মানসের প্রকাশিত রূপ যেমন প্রবৃত্তি, আচরণ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জৈবিক (Nature) ও সামাজিক (Nurture) উভয় মাত্রার প্রভাব রয়েছে। সাধারণভাবে আধুনিক মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সামাজিক মাত্রাকে প্রধান নির্ণায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু ১৮৭৪ সালে বিজ্ঞানের পৃথক একটি ধারা হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পর থেকে গত শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত নারীর মনস্তত্ব অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মূলধারার মনস্তত্ববিদগণ সমাজে আধিপত্যকারী পুরুষতান্ত্রিক ধারণার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি। এই দীর্ঘ সময়ের মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগুলোকে পর্যালোচনা করলে মনে হবে মনোবিজ্ঞান একান্তভাবে পুরুষের বা পুরুষ প্রাণীর আচরণের অধ্যয়নে কেন্দ্রীভূত আছে। কারণ ওই সময় পর্যন্ত নারীর মানসকে পৃথক একটি পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ তার অবস্থান ও বাস্তবতার নিরিখে অধ্যয়ন করার কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল না এবং মনস্তত্বের গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন মূলত পুরুষ মনস্তত্ববিদগণ। অধিকাংশ গবেষণায় বিষয়বস্তু হিসেবেও নারীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি। যেখানে নারীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে সেখানেও তাদের যৌনতা ও জেন্ডারগত পার্থক্যের বিষয়টি যথাযথভাবে উল্লেখ না থাকায় মানুষের মনের উপর এসব বিষয়ের (যৌনতা ও জেন্ডার) প্রভাবকে অনুধাবন করা যায় নি। পুরুষাধিপত্যে আক্রান্ত মনোবিজ্ঞানের এই ধারায় পুরুষের আচরণ ও মনোভাবকে আদর্শ (Norm) বলে ধরে নেয়া হয়েছে এবং সেই মানদণ্ডে বিশ্লেষিত হয়েছে নারীর মানস। নারীর মনস্তত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রচলিত ভুল ধারণা দ্বারা যেমন আক্রান্ত হয়েছে তেমনি আক্রান্ত হয়েছে এসব ধারণা দ্বারা প্রভাবিত বিজ্ঞানীদের পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত দ্বারা। উনিশ শতকের যে দুজন বিজ্ঞানীর কাজ মনোবিজ্ঞানকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তারা হলেন চার্লস ডারউইন এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েড। এই দুই বিজ্ঞানীর তত্ত্ব এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই তত্ত্বের জৈব-নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীকে ‘বিবর্তনের হীনতর ফসল’এবং ‘দুর্বলতর মানস’হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
নারী মনস্তত্ববিদেরাই মনোবিজ্ঞানের এই পুরুষ-কেন্দ্রিকতা এবং পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাত-দুষ্টতাকে প্রথম চিহ্নিত করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের অনেকেই মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় নিয়োজিত হন এবং নারীর মনস্তত্বের অধ্যয়নে মনোবিজ্ঞানের মূলধারার বাইরে এক পৃথক ধারা তৈরি করেন। পরবর্তীকালে এরাই তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও উপলব্ধি দিয়ে নারীর মনস্তত্ব সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে পেরেছিলেন। শুরুর দিকে এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন মার্কিন নারী লিটা হলিংওয়ার্থ। তিনিই প্রথম মনোবিজ্ঞানী যিনি মূলধারার মনোবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাতদুষ্ট ক্ষেত্রগুলোকে পরীক্ষা করে দেখার উদ্যোগ নেন। হলিংওয়ার্থ কিছুটা আশার আলো দেখালেও তার সময়ে নারীর মনস্তত্ব অধ্যয়নের যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পথ তৈরির প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা সহজ ছিল না। বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মূলধারার মনোবিজ্ঞানে আধিপত্যকারী অবৈজ্ঞানিক ও পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব এতটা ‘সর্বব্যাপী’ছিল যে এর প্রভাব কাটানো ছিল বেশ কঠিন। এমনকি বিশ শতকের অনেক নারী গবেষকও এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। বিশেষত যাদের উপর ফ্রয়েডের গভীর প্রভাব ছিল। তবে পরবর্তী কালে ক্যারেন হর্নাইসহ অন্যান্য নারী মনস্তত্ববিদেরাই নারীর মনস্তত্ব অধ্যয়নে ফ্রয়েডীয় চিন্তার অবৈজ্ঞানিক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। গত শতাব্দীর ৫০ ও ৬০ এর দশকে সামাজিক ডারউইনবাদী, ফ্রয়েডীয় এবং ইহুদী-খ্রিস্টান ঐতিহ্যবাদীরা নারী পুরুষের মানস সম্পর্কে প্রচলিত (পুরুষতান্ত্রিক) জেন্ডারগত ধারণার ছাঁচকেই (stereotype) নতুন করে উপস্থিত করেন। এরা সেই পুরানো জৈবনির্ধারণবাদী ‘যুক্তি’দিয়ে নারীর অধস্তনতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালান। এ সময়ে নতুন ধারার নারী গবেষকগণ বিজ্ঞানের সমসাময়িক জ্ঞান ও বোধের উপর ভিত্তি করে নতুনভাবে জৈবনির্ধারণবাদী যুক্তিকে মোকাবেলা করেছিলেন।
১৯৯০ এর দশকে নারীবাদী লেখকদের অনুসন্ধানে নারীর মনস্তত্বের অধ্যয়ন নতুন মাত্রা পায় কারণ তারা অন্যান্য গবেষকদের চেয়ে গভীরভাবে নারীর জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়েছিলেন। গত শতাব্দীতে আরেক ধারার মনস্তত্ববিদেরা নারীর মনস্তত্বের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, এটি ছিল সোভিয়েত মনোবিজ্ঞানীদের ধারা। এরাই প্রথম ফ্রয়েড ও তার অনুসারীদের পদ্ধতিগত ত্রুটি ও জৈবনির্ধারণবাদী বিচ্যুতিকে যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করেছিলেন।
এইসব নারী মনস্তত্ববিদেরা মনোবিজ্ঞানের অধ্যয়নে নারীর মানসকে ভিন্ন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখার প্রয়োজনীয়তা এবং নারীর মানসের উপর পৃথক গবেষণার বিশেষ গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমা দেশগুলোতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯৭০ এর দশকে নারীর মনস্তত্ব অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং ১৯৮০ দশকে নারীবাদী চিন্তাবিদগণ এই ক্ষেত্রে তাদের অবদান রাখতে শুরু করেন। নারীবাদী চিন্তকদের অবদান নারীর মন সম্পর্কে উপলব্ধিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। তারাই প্রথম দেখালেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাস্তবতা আসলে কেমন এবং এই বাস্তবতা কীভাবে নারীর মানস গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে। ১৯৯০ এর দশকে নারীবাদী লেখকদের অনুসন্ধানে নারীর মনস্তত্বের অধ্যয়ন নতুন মাত্রা পায় কারণ তারা অন্যান্য গবেষকদের চেয়ে গভীরভাবে নারীর জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়েছিলেন। গত শতাব্দীতে আরেক ধারার মনস্তত্ববিদেরা নারীর মনস্তত্বের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, এটি ছিল সোভিয়েত মনোবিজ্ঞানীদের ধারা। এরাই প্রথম ফ্রয়েড ও তার অনুসারীদের পদ্ধতিগত ত্রুটি ও জৈবনির্ধারণবাদী বিচ্যুতিকে যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করেছিলেন। যে দর্শনের উপর ভিত্তি করে তারা নরনারীর মানসকে উপলব্ধির পথে এগিয়েছিলেন সেটা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানুষের মনস্তত্বকে অধ্যয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা। এই দর্শন অনুযায়ী মানুষের মানসকে উপলব্ধি করতে হলে তাকে প্রথমত সামাজিক জীব হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই ধারার মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের জন্মগত মানসিক প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য থাকে কিন্তু ওগুলো তার ব্যক্তিত্বের নির্ণায়ক নয়। ব্যক্তিত্বের (personality) বিকাশ তখনই শুরু হয় যখন সে অন্য মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে নিয়োজিত হয়। অতএব, নরনারীর ব্যক্তিত্বের পার্থক্য তৈরির ক্ষেত্রেও তাদের পৃথক সমাজ-বাস্তবতা গুরুত্বপূর্ণ । এভাবে নারীবাদী ও বস্তুবাদী ধারার বিকাশের ফলেই গত শতাব্দীতে নারীর মনস্তত্বকে উপলব্ধি করার পরিণত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে ওঠে।
(২)
পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-বাস্তবতা নারীপুরুষের মানসকে কতটা বদলে দেয় তা বুঝতে হলে প্রকৃতিগতভাবে বা জন্মগতভাবে নারীপুরুষের মানসিক প্রবণতার পার্থক্য কতটুকু থাকে কীভাবে তার সঙ্গে সামাজিক ও অন্যান্য পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়া ঘটে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এক্ষেত্রে আধুনিক জীববিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণের দিকেই আমাদের তাকাতে হবে। মনের অস্তিত্ব পুরোপুরিই মস্তিষ্কের ভেতরে। শরীরের অন্যান্য অংশে যেমন নারীপুরুষের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে, মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যপ্রণালীতেও রয়েছে বেশ কিছু ভিন্নতা। জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক যেসব উন্নতি হয়েছে তার ফলে আমরা মানসিক প্রবণতার জৈবিক-ভিত্তি সম্পর্কে অনেক সুনির্দিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত পাচ্ছি। তবে এসব তথ্য ও উপাত্তকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। মাত্রাজ্ঞান ও বাস্তবতার নিরিখে বিচার না করার ফলে অতীতে অনেকেই এসব বিষয়ে জৈব-নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যায় উপনীত হয়েছেন। সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট এসব ব্যাখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, দাসপ্রথা ইত্যাদি নানা ধরণের প্রচলিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার পক্ষে।
জন্মের পর যে বয়স পর্যন্ত শিশুদের উপর সমাজের বিশেষ কোনো প্রভাব থাকে না সে বয়সের মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুর উপর বিভিন্ন মনস্তাত্বিক গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, জন্মগতভাবে বা প্রকৃতিগতভাবে নারীপুরুষের মানসিক প্রবণতায় কিছুটা ভিন্নতা থাকে। জৈবিক এই পার্থক্য নারী ও পুরুষের পৃথক মানসিক গঠনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখলেও শুধু জৈবিক ছাঁচে তাদের মানস গড়ে ওঠে না। এর ভিত্তিতে বড়জোর আমরা বলতে পারি জৈবিকভাবে তাদের (নারীপুরুষের) প্রকৃতির তার এমনভাবে বাঁধা যে তাদের মধ্যে মানসিকভাবে একটি নির্দিষ্ট প্রকারের হবার প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা (potential) রয়েছে। যে কোনো জীব বা জৈবসত্ত্বার (individual) ক্ষেত্রে এই প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাকে বলা হয় জৈবনিক সম্ভাবনা (Biological potential)। মস্তিষ্কের মানস-নিয়ন্ত্রণকারী অংশের জৈবনিক সম্ভাবনার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়ায় প্রতিটি নারীপুরুষের পৃথক মানসিক প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব ও আচরণের নির্দিষ্ট ধরণ গড়ে ওঠে।
জীবনবৃক্ষে মানুষ প্রাইমেট বর্গের অন্তর্গত। গবেষণায় দেখা গেছে প্রাইমেটদের মধ্যে যে প্রজাতির ক্ষেত্রে সামাজিক বন্ধন যত কম তাদের মানসিক প্রবণতায় জৈবিক প্রবৃত্তির প্রভাব ততো বেশি। মানুষের ক্ষেত্রে সামাজিক বন্ধন সবচেয়ে শক্তিশালী, জটিল ও স্থায়ী। সামাজিক প্রভাবের কারণে মানুষের যে কোনো বৈশিষ্ট্যের জৈবনিক-সম্ভাবনা বড় ধরনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায় এবং পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হয়। মস্তিষ্কের গঠনের দিক থেকে নারীর মধ্যে যে মানসিক প্রবণতা থাকার জৈবনিক সম্ভবনা রয়েছে বাস্তবে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে তার থেকে বেশ ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। গত শতাব্দীতে বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে নৃতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধান ও গবেষণা থেকে দেখা গেছে সামাজিক অবস্থার ভিন্নতার কারণে ভৌগলিকভাবে কাছাকাছি বসবাসকারী বিচ্ছিন্ন কয়েকটি জনগোষ্ঠীর নারীপুরুষের মানসিক প্রবণতার মধ্যে বড় ধরনের ভিন্নতা রয়েছে। কেবল মস্তিষ্কের গঠনের জৈবনিক সম্ভাবনা অনুযায়ী নারীপুরুষের মানসিক প্রবণতা গঠিত হয়ে থাকলে সকল সমাজেই এর একটি সার্বজনীন রূপ থাকার কথা।
আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি ধারণা হল নারীর ক্ষেত্রে সন্তান-বাৎসল্য পরিপূর্ণভাবে একটি জৈবিক ব্যাপার এবং এর প্রভাব অনেক শক্তিশালী। সে কারণে তার ক্ষেত্রে এর অন্যথা (বাৎসল্য-বিরোধী) হওয়া সম্ভব নয় বা ‘প্রাকৃতিক’ নয়। এটি নারীর প্রকৃতিগত ‘গভীরতম প্রবণতা’ এমন ধারণা থেকে অনেক জীববিজ্ঞানীও মুক্ত নন। সন্তান ধারণ ও সন্তান পালনের সময় নারীর শরীরে হরমোনগত পরিবর্তন ঘটে এবং এই হরমোনগুলি মস্তিষ্কের সেই অংশগুলোকে উদ্দীপ্ত করে যেগুলোর সক্রিয়তা সন্তানের প্রতি মনোযোগ ও আগ্রহ বাড়ায়। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে সন্তানের প্রতি তীব্র মায়া বা টান সামাজিকভাবে তৈরি হওয়া একটি বিষয়। মানব প্রজাতির ক্ষেত্রে উন্নত সমাজে, যেখানে শিশুকে জন্ম দেওয়া, খাওয়ানো, প্রকৃতির প্রতিকুলতা থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক সহায়তা পাওয়া যায় সে সমাজের নারীদের মাতৃ-মানসিকতা এবং বন্য-অবস্থায় প্রতিকূল আদিবাসী সমাজের নারীদের মাতৃমানসিকতা এক নয়। মা-কর্তৃক শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করা এবং হত্যা করার ঘটনা এখনও অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়মিত একটি ব্যাপার। সন্তান জন্মের সময় উভয় সমাজের নারীদের একই ধরনের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু মাতৃমানসিকতার ক্ষেত্রে বড় ধরণের পার্থক্যের কারণ হচ্ছে এই মানসিকতা পরিপূর্ণভাবে জৈবিক নয় বরং জৈবিক ও সামাজিক বাস্তবতার মিথষ্ক্রিয়ায় সৃষ্ট।
মস্তিষ্কের মানস নিয়ন্ত্রণকারী অংশ এবং এই অংশের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী শারীরতাত্ত্বিক জৈব-রসায়নের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে কিন্তু তা অপরিবর্তনীয় ও স্থির কোনো বিষয় নয়। এই পার্থক্য সত্ত্বেও বেশিরভাগ নারীপুরুষ যেকোনো মানসিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে অসচেতনতার কারণেই নারীপুরুষের মানসের পার্থক্যকে অনেক সময় ভুলভাবে জৈবিক পার্থক্য বলে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে জৈবিক পার্থক্যের একরৈখিক বিচার জন্ম দেয় জৈব-নির্ধারণবাদী বিভ্রান্তির। এসব বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত না হলে নারীর মন সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়।
(৩)
নারীপুরুষের মানসের প্রকৃত রূপ যাই হোক আমাদের সমাজে এ সম্পর্কে যে বিশ্বাসগুলো প্রচলিত রয়েছে তার ভিত্তিতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীপুরুষের ব্যক্তিত্ব ও সক্ষমতাকে বিচার করা হয়। এই প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসগুলো কেমন তার স্বরূপ দেখার গুরুত্বপূর্ণ আয়না হল ওই সমাজে প্রচলিত রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা, কিংবদন্তী ইত্যাদি। এগুলোর স্রষ্টা সমাজের অনেকে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সমাজের বহুসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণে তাদের চিন্তা, ধারণা ও উপলব্ধির ছায়া রয়েছে এই জনপ্রিয় কাহিনীগুলোর মধ্যে। এসব কাহিনীতে নারী ও পুরুষের মানসিকতার যে চিত্র আমরা পাই তা নারী পুরুষের মানস সম্পর্কে সামাজিক বিশ্বাসকে অনেকটাই প্রতিফলিত করে।
এসব কাহিনীর মাধ্যমে নারীর মানস সম্পর্কে সমাজে আবহমান কাল থেকে যে বিশ্বাসের ছাঁচ (Stereotype) ছিল সেখানে নারীর মানস সম্পর্কে বিশ্বাসের দুটো ধরণ আমরা দেখতে পাই। একটা ধরণ হল ‘ভাল’ নারী যার মানস দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় (Passive)। এরা প্রতিবাদ করতে পারে না কিংবা দুরবস্থা থেকে মুক্ত হবার মনোবল বা আত্মশক্তি তাদের নেই। তাই তারা আক্রান্ত বা উপদ্রুত হয় বা মরে যায়। অন্য একটা ধরণ হল ‘খারাপ’ নারী। মানসিকতার দিক থেকে এরা হিংসুটে, পরশ্রীকাতর, নিষ্ঠুর, অমানবিক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং সক্রিয়। অন্যদিকে এসব কাহিনীতে প্রতিফলিত পুরুষের মানস সক্রিয়, প্রতিদ্বন্দ্বীতা-পরায়ণ, স্বনির্ভর এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান। বর্তমান সময়ে সেই পুরাণ সমাজের ধারণা ও বিশ্বাস কিছুটা পাল্টে গেলেও বহুলাংশে টিকে আছে। লাজুক, ভীরু, নির্ভরশীল, সংকীর্ণ, আপোষকামী, ঈর্ষাকাতর, হুজুগে ইত্যাদি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এবং ভদ্র, কোমলমনা, আবেগপ্রবণ, মমতাময়ী, ‘নির্বিবাদী’ ইত্যাদি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য নারীর মানসের প্রকৃতিগত (Innate)ধরণ এমন বিশ্বাস আমাদের সমাজে এখনও মোটামুটি সার্বজনীন। অন্যদিকে সাহসী, সক্রিয়, প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও সংঘাত-পরায়ণ, স্বনির্ভর, চিন্তাশীল এবং আত্মশক্তিতে বলীয়াণ ইত্যাদি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য এবং বেপরোয়া, আক্রমণাত্মক, নিষ্ঠুর ইত্যাদি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পুরুষের মানসের প্রকৃতিগত ধরণ এমন বিশ্বাসও একইভাবে টিকে আছে। এই সমাজের মধ্যে বেড়ে ওঠা নারীপুরুষ এই বিশ্বাসের ছাঁচেই কমবেশি নারী ও পুরুষের মানসিকতাকে চিহ্নিত করে থাকে। এই বিশ্বাসগুলো সাধারণত সমাজের নারীপুরুষের আচরণের অগভীর ও মোটাদাগের পর্যবেক্ষণ থেকে গড়ে ওঠে।
এ যুগের মনস্তত্ববিদগণ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের উপর যে গবেষণা চালিয়েছেন তাতেও দেখা গেছে নারীপুরুষের মানস সম্পর্কে প্রচলিত বর্তমান সমাজে প্রচলিত ধারণাগুলো রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা, কিংবদন্তীতে প্রকাশিত ধারণার কাছাকাছি। তারা দেখেন- নারীদের সম্পর্কে বিশ্বাস এমন যে এরা অভিব্যক্তিপূর্ণ, স্বার্থপরায়ণ, আবেগপ্রবণ, মার্জিত, সহানুভূতিশীল এবং নিবেদিতপ্রাণ। অন্যদিকে পুরুষকে অধিক দৃঢ়প্রত্যয়ী বলে বিশ্বাস করা হয় বলে তাদের চিহ্নিত করা হয় অধিক সক্রিয়, সক্ষম, প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ, স্বাধীনচেতা এবং আত্ম-প্রত্যয়ী হিসেবে। সমাজে নারীপুরুষ ও বালক বালিকাকে প্রতিদিন তারা যেভাবে জীবন যাপন করতে দেখে মূলত তার উপর ভিত্তি করে একধরণের ভাসা ভাসা বোধ থেকেই এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে। এইসব বিশ্বাসের পূর্বসূত্র বা সামাজিক ভিত্তি আমরা দেখতে পাই না। যেমন- অধিকাংশ নারী বা বালিকার মনের মাঝে ভীতি, সংকোচ বা লাজুকতা পুরুষের তুলনায় বেশি দৃশ্যমান হয় তার পূর্বসূত্র হিসেবে নারীদের ক্ষেত্রে নানা রকম অবরোধ ও নিপীড়নের ভয় ও আশঙ্কা ইত্যাদি আমাদের বিবেচনায় থাকে না। সামাজিক বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানসিকতা ও আচরণগুলো যখন প্রশ্রয় পায় বা পুরষ্কৃত হয় এবং বিশ্বাসের বিপরীত মানসিকতা যখন ধিকৃত বা শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয় তখন এই ধারণাগুলো আরও গভীরে প্রোথিত হবার সুযোগ পায়। বিশ্বাসগুলো নানা ভাবে সমাজে বেড়ে ওঠা নারীপুরুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমাদের কথিত ও লিখিত ভাষা, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী, সমবয়সীদের কাছ থেকে পাওয়া ধারণা, মিডিয়া ইত্যাদি। বেশিরভাগ মানুষ এই বিশ্বাসের ছাঁচেই নারী ও পুরুষের মানসকে বিচার করে। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নারী পুরুষ উভয়ের উপরেই পরে। তারা সচেতন বা অবচেতনভাবে এই ছাঁচের আদলে নিজেদের মানসিকতা ও আচরণকে পরিবর্তন করে এবং অন্যদের ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেয় এবং এর বিপরীত কিছু হলে তাকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়।
(৪)
গত শতাব্দীতে আধুনিক মনোবিজ্ঞান সূত্রায়িত করে- মানুষের জন্মগত মানসিক প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলো তার ব্যক্তিত্বের নির্ণায়ক নয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ তখনই শুরু হয় যখন সে অন্য মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে নিয়োজিত হয়। তাই বেশিরভাগ মেয়ের মধ্যে ‘মেয়েলী আচরণ’ বা ‘মেয়েলী স্বভাব’ ইত্যাদির উপস্থিতি দেখা গেলেও অনুমান করা যায় সেগুলো তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য নয় এবং নরনারীর ব্যক্তিত্বের পার্থক্য তৈরির ক্ষেত্রেও সমাজ-বাস্তবতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারী ও পুরুষকে ভিন্ন রকমের সামাজিক বাস্তবতা ও সম্পর্কের মধ্যে যেতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট ভূমিকার সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য শৈশব থেকেই মেয়েরা নিজেদের প্রস্তুত করতে বাধ্য হয়। এভাবে প্রস্তুত না হলে পুরুষতান্ত্রিক পরিবার ও সমাজের সম্পর্কগুলো তার জন্য সাংঘর্ষিক হয় এবং এর জন্য নারীকেই মূল্য দিতে হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে অনেক অল্প বয়সেই মেয়েরা নারীসুলভ আচরণ সম্পর্কে সামাজিক প্রত্যাশা ও নির্দেশনাগুলো অনুধাবন করতে পারে যা তাদের মানসিক বিকাশের গতি-প্রকৃতিকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। লিঙ্গ-নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কিত ধারণাগুলো মেয়েরা পায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। তবে এগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উৎস হল পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গুরুত্বের দিক থেকে এরপরেই রয়েছে সামাজিক কালচার ও মিডিয়ার ভূমিকা।
বেড়ে ওঠার সময় শিশু সবার আগে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের মনোভঙ্গি ও আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মা-বাবা। এই প্রভাব প্রধানত দুই রকমের। প্রথমত, মেয়েসন্তান তার মায়ের আচরণ ও মনোভঙ্গিকে নিজের অজান্তেই অনেকটা অনুসরণ করতে থাকে। অন্যদিকে মেয়েসন্তান সম্পর্কে মা বাবার ধারণা এবং তারা কন্যা সন্তানের কাছ থেকে কেমন আচরণ আশা করছেন সেটাও বেড়ে-ওঠা মেয়েটির আচরণকে সুনির্দিষ্ট আকার দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে বেশিরভাগ বাবামায়ের বিশ্বাস কাঙ্ক্ষিত আচরণ ও জীবনধারার বাইরে গেলে মেয়েরা সমূহ বিপদে পড়তে পারে। এ কারণে মা-বাবা ছেলেমেয়েদেরকে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আচরণ, কাজকর্ম, পোশাক ও খেলায় উৎসাহিত করেন এবং তাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট বিশ্বাস সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। মা বাবার কাছ থেকেই ধর্ম, লোকাচার এবং অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস আর আচারের প্রভাব ছেলেমেয়ের কাছে আসে। ধর্মে মেয়েদেরকে অবদমিত ও গন্ডীবদ্ধ রাখার যে বিধান বা আচার রয়েছে পারিবারিক বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই তা মেয়েদের জীবনে আরোপিত হয়। যা তাদের জীবনকে আরও সীমাবদ্ধ করে এবং তাদের বাস্তবতাবোধ ও আত্মবিশ্বাসকে খর্ব করে। নারীর মনের উপর পরিবারের এই প্রভাব সাধারণত গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী হয়।
বালিকাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আচরণে প্ররোচনা দেয় প্রধানত সমবয়সীরা এবং শিক্ষকেরা। মা বাবার মতো শিক্ষকেরাও বালিকাদের উপর অনেক লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আচরণ ও কর্মকাণ্ড চাপিয়ে দেন। কারিকুলামের বাইরেও স্কুলে একটা ‘অদৃশ্য কারিকুলাম’ থাকে যা বালিকাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আচরণের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতিকে আরোপ করে শিক্ষার্থীদের আচরণের কোড নির্ধারণ করে যা মেয়েদের উপর কঠোরভাবে চাপানো হয়।
বালিকাদের সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। নারীর মানসিকতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবারের পরেই রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। তাদের ওপর শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের সমবয়সী মেয়েদের মতো, আচরণ ও পছন্দ-অপছন্দের গভীর প্রভাব থাকে। বালিকাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আচরণে প্ররোচনা দেয় প্রধানত সমবয়সীরা এবং শিক্ষকেরা। মা বাবার মতো শিক্ষকেরাও বালিকাদের উপর অনেক লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আচরণ ও কর্মকাণ্ড চাপিয়ে দেন। কারিকুলামের বাইরেও স্কুলে একটা ‘অদৃশ্য কারিকুলাম’ থাকে যা বালিকাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আচরণের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতিকে আরোপ করে শিক্ষার্থীদের আচরণের কোড নির্ধারণ করে যা মেয়েদের উপর কঠোরভাবে চাপানো হয়। সহপাঠিদের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে মেয়েদের মধ্যে সমলিঙ্গ ও বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের মানদণ্ড তৈরি হয়। এখানেই তাদের মধ্যে জেন্ডারের ভিত্তিতে সামাজিক কার্যক্রমে যুক্ত হবার প্রবণতা তৈরি হয়। দেখা গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমবয়সীদের মধ্যে নারী এবং পুরুষ উভয়েই লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আচরণকে পছন্দ করে এবং উৎসাহ দিয়ে থাকে। যেমন দেখা গেছে জনপ্রিয়তার রেটিং-এ বেশি নম্বর পেয়েছে সেই তরুণী যার মধ্যে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বেশি। অল্প বয়স থেকেই নারীর উপর চেপে বসা এই ‘নারীসুলভ’ আচরণ তার মধ্যে যে উদ্যোগহীনতা এবং বাধ্যতাকে আরোপ করে। এটা আরও শক্তিশালী হয় সমবয়সী পুরুষদের সঙ্গে মেশার ফলে। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে বেশি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা পুরুষের অধীনস্ত পদ মেনে নিচ্ছে।
মিডিয়া যেভাবে নারীপুরুষের আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরে তা বেশিরভাগ বালিকা ও তরুণীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ও হীনমন্যতার জন্ম দেয়। তবে আশার কথা হল, মেয়েরা যত পরিণত হয় ততই তাদের উপর চেপে থাকা লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আচরণের বন্ধন শিথিল হতে থাকে।
এ যুগে গণমাধ্যম লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আচরণ ও কর্মকাণ্ডের শক্তিশালী প্ররোচক। মূলধারার চলচিত্রের নায়িকা, ডিজনির কার্টুনের রাজকন্যা, টিভি শোর এর উপস্থাপক বা বিজ্ঞাপনের মডেল সবার কাছ থেকেই এই বালিকারা লিঙ্গ-নির্দিষ্ট ভূমিকা ও আচরণ সম্পর্কে ধারণা পেতে থাকে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- নারী চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ, পারিবারিক আচরণ, নারীদের পেশা ও বৃত্তি এবং নারীপুরুষের শারীরিক অবয়ব সম্পর্কিত ধারণাগুলো। মিডিয়া যেভাবে নারীপুরুষের আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরে তা বেশিরভাগ বালিকা ও তরুণীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ও হীনমন্যতার জন্ম দেয়। তবে আশার কথা হল, মেয়েরা যত পরিণত হয় ততই তাদের উপর চেপে থাকা লিঙ্গ-নির্দিষ্ট আচরণের বন্ধন শিথিল হতে থাকে। ফলে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট মানসিক প্রবণতা, যার অনেকটাই অল্প বয়সে সমবয়সীদের প্রভাবে নারীর মধ্যে আরোপিত হয়েছিল, সেগুলো কাটিয়ে ওঠা তার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।
(৫)
মানুষের সমাজে যেকোনো বৈষম্যমূলক ও অসম ক্ষমতা-সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত সহিংসতা ও নিপীড়নের উপর নির্ভর করতে হয়। অধস্তন ও অবদমিত গোষ্ঠী হিসেবে নারীও এর ব্যতিক্রম নয়। নারীকে তার অধস্তন অবস্থান এবং অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্যে রাখার ক্ষেত্রেও পুরুষতান্ত্রিক পরিবার এবং সমাজের কাছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে সহিংসতা ও নিপীড়ন। এ সমাজে মোটের উপর প্রতি তিনজনে একজন নারী সহিংসতা ও নিপীড়নের শিকার হন এবং তাদের ব্যাপক অধিকাংশই এগুলোর ভীতি ও হুমকির মধ্যে থাকেন। এই ভীতি ও হুমকি যে সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করে তা নারীর মানসিক প্রকৃতির গঠনে এবং এর গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
এ সমাজের বাস্তবতা এমন যে নারীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে নাজুক, দুর্বল এবং গ্লানির জায়গা হচ্ছে তার যৌনতা এবং যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অতএব, নারীকে সবচেয়ে নির্মমভাবে আঘাত করার উপায় হচ্ছে যৌন নিপীড়ন। যৌন-নিপীড়ন যার দ্বারাই সংঘটিত হোক সমাজের দৃষ্টিতে এর মুখ্য গ্লানি আক্রমণকারীর নয় আক্রান্ত নারীর। পশ্চাৎপদ সমাজে এই গ্লানি বা ‘কলঙ্ক’ এমন এক গ্লানি যা কোনো কিছু দ্বারাই মোচনীয় নয়। যে সমাজ যত পশ্চাৎপদ সে সমাজে এই মনোভাব তত গভীর। যৌন-নিপীড়নের নেতিবাচক প্রভাব নারীকে অত্যন্ত নির্মম ও গভীরভাবে অক্রান্ত করে যার ফলে অনেক নারীই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
নারীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে নাজুক, দুর্বল এবং গ্লানির জায়গা হচ্ছে তার যৌনতা এবং যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অতএব, নারীকে সবচেয়ে নির্মমভাবে আঘাত করার উপায় হচ্ছে যৌন নিপীড়ন। যৌন-নিপীড়ন যার দ্বারাই সংঘটিত হোক সমাজের দৃষ্টিতে এর মুখ্য গ্লানি আক্রমণকারীর নয় আক্রান্ত নারীর।
নারীর মধ্যে অন্তর-মুখীতা, আক্রান্ত হবার ভীতি, ঝামেলা এড়িয়ে চলার প্রবণতা, ‘রহস্যময়ীতা’ (নিজের মনোভাব আড়াল করার প্রবণতা), সংকোচ ও লাজুকতা ইত্যাদির অনেকটা আসে পুরুষতান্ত্রিক সহিংসতা ও নিপীড়নের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রচেষ্টা থেকে এবং কিছুটা আসে বয়োজ্যেষ্ঠ নারীদের দিক নির্দেশনা থেকে। ছোটবেলা থেকে মেয়েদের অভিজ্ঞতা হয়- প্রতিবাদী, মেনে না-নেওয়া, বহির্মুখী নারীদেরকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের সহিংস আচরণ এবং নিপীড়নের শিকার হতে হয়। এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে তাদের আচরণের মধ্যে নির্বিবাদী হওয়া, মানিয়ে নেয়া, ছলনা বা কায়দা করে কথা বলা বা ভাব প্রকাশ করা, ‘সহজে’ গুটিয়ে যাওয়া, ঝুঁকি নিতে আগ্রহী না হওয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ক্রীতদাস, যুদ্ধবন্দী ও অন্যান্য বন্দী, নিচু জাতের মানুষেরা যে ধরণের নির্মম নিষ্পেষণের শিকার হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীও যে এরকম বন্দীত্ব, নিষ্পেষণ ও দাসত্বের মধ্যে থাকে তা প্রায়ই আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। তুচ্ছ কারণে নারীকে হত্যা করা এবং তার দেহ ও মনের চরম নিগ্রহের এসব নিদর্শন আমাদের সামনে মূর্ত করে তোলে তাদের বন্দীত্ব ও দাসত্বের শেকড় কত গভীরে প্রোথিত। ইউরোপের ‘উইচ হান্ট’ অর্থাৎ অপয়া সন্দেহে নারীদের নির্মমভাবে নির্যাতন ও হত্যা, আমাদের দেশে হিন্দু সমাজের সহমরণ প্রথায় নারীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা এবং পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য চীনের মেয়েদের চরম যন্ত্রণাদায়ক পায়ের পাতার বাঁধন মানব ইতিহাসে নারীর উপর ঘটে যাওয়া কিছু চরম নির্যাতনের ঘটনা।
গত শতাব্দীতে মনস্তাত্বিক গবেষককেরা লক্ষ্য করেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রকাশিত মনোভাব, ব্যক্তিত্ব ও আচরণসমূহকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর ধরণ হচ্ছে দাসত্ব, অবদমন ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষের মনোভাবের মতো। পঞ্চাশের দশকে মার্কিন মনস্তত্ববিদ হেলেন মায়ার হ্যাকারের গবেষণায় উঠে আসে- গোষ্ঠীগত ভাবে নারীদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই আফ্রিকান-আমেরিকানদের আচরণ ও মনোভঙ্গীর মিল রয়েছে; যেমন, অধিক আবেগময় ও শিশুসুলভ ব্যবহার, নিজেকে হীনতর হিসেবে প্রকাশ করা, অসহায়ত্ব বা দুর্বলতা প্রকাশ করা, ছলনাময় ও দুর্বোধ্য আচরণ করা ইত্যাদি। তাঁর ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয় যে- এগুলো জন্মগত কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। উভয় জনগোষ্ঠীর উপর একইভাবে বিদ্যমান বন্দীত্ব, অবদমন এবং (নিয়মিত) সহিংসতা ও নিপীড়নের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য এক ধরণের অভিযোজনমূলক প্রতিক্রিয়া থেকে গড়ে ওঠে এ ধরণের আচরণ।
সত্তর ও আশির দশকে মনস্তাত্বিক জে বি মিলার এবং জ্যাঁলিম্পেন-ব্লুমেনের লেখাতেও নিপীড়িত গোষ্ঠীর সঙ্গে নারীর মানসের সাদৃশ্যের বিষয়টি উঠে এসেছে। তারা দেখান ক্ষমতাহীন গোষ্ঠীর লোকেরা ক্ষমতাসীনদের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে তাদের বুদ্ধি, চালাকি, স্বজ্ঞা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যৌনতা, ছলাকলা, এড়িয়ে চলা ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করে। তারা আরও দেখান যে- অধিনস্ত নারীরা আধিপত্যকারীদের (পুরুষ) স্বরগ্রামে এতটা গভীরভাবে বাঁধা পড়ে যে কোনটা তাদের (আধিপত্যকারীদের) সন্তুষ্ট করবে এবং কোনটাতে তারা অসন্তুষ্ট হবে তা তাদের অন্তরাত্মার মধ্যে ঢুকে যায়। এধরণের আচরণের মধ্যে রয়েছে- অধিক আবেগময় ও শিশুসুলভ ব্যবহার, নিজেকে হীনতর হিসেবে প্রকাশ করা, অসহায়ত্ব বা দুর্বলতা প্রকাশ করা, ছলনাময় ও দুর্বোধ্য আচরণ করা ইত্যাদি।
(৬)
পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজের শরীর নিয়ে নারীকে দুধরণের জটিল চক্করে পড়তে হয়। একটি সাধারণ ধারণাই এই দুই চক্করের মূল উৎস। এটি হল- নারীর দেহ পুরুষের ভোগের বস্তু এবং এ সমাজে এটিই নারীর অস্তিত্বের প্রধান পরিচয়। তাই পুরুষের ভোগের বস্তু হিসেবে নারীর উৎকর্ষই এ সমাজের দৃষ্টিতে তার ব্যক্তিগত উৎকর্ষের প্রধান নির্ণায়ক। শারীরিক সৌন্দর্য এবং যৌন আবেদনই এই সমাজে নারীর গ্রহণযোগ্যতার মুখ্য মাপকাঠি, আর সব গুণই গৌণ। অতএব ছেলেবেলা থেকেই মেয়েরা শরীরী সৌন্দর্য অর্জন ও রক্ষার এক চক্করে পরে। যা হয়ে যায় তার অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। পুরুষের ভোগের বস্তু হিসেবে অন্য যে চক্করে সে পরে তা হল- তার শরীর ভোগের বৈধ অধিকর্তা (স্বামী বা রক্ষক) ছাড়া অন্য সকল পুরুষের ‘ভোগ বা ভোগের লালসা’ থেকে নিজেকে ‘রক্ষা’ করার চক্কর। এর জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার উপর আরোপ করে বাধ্যতামূলক অবরোধ। শরীর ঢাকার কঠোর বাধ্যবাধকতা এবং চলাফেরা ও সামাজিক মেলামেশার উপর কঠোর শৃঙ্খল এই চক্করের মূল স্বরূপ, তবে যাপিত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এর প্রয়োগ অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অমানবিক ও নির্মম। এই উভয় চক্কর একদিকে যেমন মেয়েদের জীবনে নিয়ে আসে অমানবিক ও কষ্টদায়ক এক বাস্তবতা, অন্যদিকে তাকে বেঁধে ফেলে কঠিন এক মানসিক চাপের জালে। শরীর ও অস্তিত্বকে ঘিরে এই দ্বিবিধ চক্করের করুণ বাস্তবতা নারীর মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।
পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নারীর সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায় তা সার্বজনীন নান্দনিক কিছু নয়। বরং নির্দিষ্ট একটি সমাজে সৌন্দর্যের নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড থাকে, সেই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলেই তাকে সুন্দর বলা হয়। এই মানদণ্ড অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি হয়, তবে এর প্রধান দিক হল যৌন আবেদন। পশ্চিমের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের যে মাপকাঠি তার থেকে ভিন্ন আফ্রিকার গরীব দেশের সমাজের মাপকাঠি। কিন্তু যে ব্যাপারটি দুই সমাজেই এক তা হল- উভয় সমাজে নারীরাই নিজ নিজ সমাজের আদর্শ সৌন্দর্য ও যৌন আবেদনের অবাস্তব মানদণ্ডে উন্নীত হবার জন্য এক কষ্টকর ও যন্ত্রণাবিদ্ধ যাত্রায় নিবেদিত হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখেছি পুরুষের দৃষ্টিতে ‘সুন্দর’ ও যৌন আবেদনময়ী হবার জন্য নারীকে অবর্ণনীয় শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে যেতে হচ্ছে। অনেক সময় মেয়েরা স্বেচ্ছায় এই যন্ত্রণার মধ্যে যায় কিন্তু বল প্রয়োগে তাদেরকে এই যন্ত্রণায় যেতে বাধ্য করা হচ্ছে এমন নিদর্শনও কম নয়।
‘বিশেষ ক্যাম্প’ করে বালিকাদের একদিনে দৈনিক তার স্বাভাবিক চাহিদার সাত থেকে দশগুণ খাবার খাওয়ানো হয়। কয়েক মাস ব্যাপী এই জোর করে খাওয়ানো মেয়েদের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ও অস্বস্তিকর ব্যাপার। এতে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পরে। পুরুষের ভোগের উপযোগী করার জন্য নারীর ব্যক্তিসত্তাকে অগ্রাহ্য করে এভাবেই, তাকে শারীরিকভাবে অনেকাংশে অক্ষম এবং মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়।
মানব ইতিহাসে সৌন্দর্যের জন্য জোরপূর্বক শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা চাপিয়ে দেবার একটি চরম উদাহরণ হচ্ছে ছোট বেলা থেকে চীনের মেয়েদের পায়ের পাতার যন্ত্রণাদায়ক বাঁধনের প্রথা। দশম শতক থেকে গত শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় একহাজার বছর টিকে ছিল এই নির্মম প্রথা। ছোটবেলায় এই নির্মম প্রথা চাপিয়ে দেওয়ায় তার মনের ওপর কি প্রভাব পড়েছিল সে সম্পর্কে এক বৃদ্ধ চীনা নারী বলেন- ‘আমি ছিলাম দুরন্ত এবং লাফ ঝাঁপ দিতে পছন্দ করা একটি বাচ্চা কিন্তু ঐ সময় থেকে আমার মুক্ত ও আশাবাদী মনটা মরে গেল।’ এই একুশ শতকেও বলপূর্বক কিশোরীদের সৌন্দর্য বড়ানোর যন্ত্রণাদায়ক প্রথা আফ্রিকার বেশ কটি অনগ্রসর দেশে রয়ে গেছে। ‘বিশেষ ক্যাম্প’ করে বালিকাদের একদিনে দৈনিক তার স্বাভাবিক চাহিদার সাত থেকে দশগুণ খাবার খাওয়ানো হয়। কয়েক মাস ব্যাপী এই জোর করে খাওয়ানো মেয়েদের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ও অস্বস্তিকর ব্যাপার। এতে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পরে। পুরুষের ভোগের উপযোগী করার জন্য নারীর ব্যক্তিসত্তাকে অগ্রাহ্য করে এভাবেই, তাকে শারীরিকভাবে অনেকাংশে অক্ষম এবং মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। যেন সে মানুষ নয় পুরুষের ভোগের বস্তু মাত্র, এর জন্য অধিক উপযোগী করতে তাকে যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবে কেটে ছিঁড়ে তৈরি করে নেয়া যাবে।
‘সভ্য’ ও ‘উন্নত’ বলে পরিচিত আধুনিক দেশগুলোতে সৌন্দর্যের জন্য নারীদের উপর পরিবার ও সমাজের প্রত্যক্ষ জবরদস্তি কমে গেছে কিন্তু সৌন্দর্যের ভূত অন্যভাবে নারীর ঘাড়ে চেপেছে। ফ্যাশন ও কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রির বাণিজ্য এবং ‘সর্বত্রগামী’ প্রচার মাধ্যমের উপর সওয়ার হয়ে সৌন্দর্য চর্চার পুরানো বৃক্ষ বহু শাখা-প্রশাখা মেলেছে।
‘সভ্য’ ও ‘উন্নত’ বলে পরিচিত আধুনিক দেশগুলোতে সৌন্দর্যের জন্য নারীদের উপর পরিবার ও সমাজের প্রত্যক্ষ জবরদস্তি কমে গেছে কিন্তু সৌন্দর্যের ভূত অন্যভাবে নারীর ঘাড়ে চেপেছে। ফ্যাশন ও কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রির বাণিজ্য এবং ‘সর্বত্রগামী’ প্রচার মাধ্যমের উপর সওয়ার হয়ে সৌন্দর্য চর্চার পুরানো বৃক্ষ বহু শাখা-প্রশাখা মেলেছে। ‘নিখুঁত’ সৌন্দর্য পাবার জন্য শরীরের এমন কোনো অঙ্গ নেই যার পরিচর্যা এ যুগের নারীরা করে না। বলাবাহুল্য তাদের এই সৌন্দর্য চর্চারও মুখ্য উদ্দেশ্য পুরুষতান্ত্রিক মানদণ্ডে অধিক যৌন-আবেদনময়ী হওয়া। আধুনিক এই ‘চর্চা’ একদিকে গভীর ও বিস্তৃত অন্যদিকে যন্ত্রণাদায়ক এবং ব্যয়বহুল। শরীরকে সৌন্দর্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করার জন্য এযুগে যে সব অঙ্গ ও অংশে পরিবর্তন আনা হয় সেগুলো হচ্ছে- চুল, ভুরু, চোখ, নাক, কান, ঘাড় ও কাঁধ, ঠোঁট, থুতনি, বগল, কব্জি, হাতের নখ, স্তন ও স্তনের বোটা, পেট, নাভী, যৌনাঙ্গ, নিতম্ব, উরু, পা (Leg), পায়ের পাতা (Foot), পায়ের নখ ইত্যাদি।
খুব ছোটবেলা থেকেই মেয়েরা সৌন্দর্য রক্ষা ও সৌন্দর্য বাড়ানোর নানা দক্ষযজ্ঞের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এগুলো তার মধ্যে আসে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নারী এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতা থেকে। কসমেটিক ও ফ্যাশান ইন্ডাস্ট্রির প্ররোচণায় মিডিয়া ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই বাসনা আরও প্রবল হয়। নারীর বাহ্যিক অবয়ব কেমন হবে সৌন্দর্যের মানদণ্ডগুলো শুধু সে নির্দেশ দেয় তাই নয়, এগুলো নারীর চলাফেরা, দেহভঙ্গী, কথাবলা এবং আচার-আচরণ ইত্যাদির মানদণ্ডও তৈরি করে দেয়। এই মানদণ্ডই বলে দেয় ব্যক্তি নারীর সঙ্গে তার শরীরের সম্পর্ক কেমন হবে। এসব নির্দেশনা নারীর শারীরিক স্বাধীনতার উপর এমন অনেক সীমাবদ্ধতা আরোপ করে যা তার সমবয়সী পুরুষের ক্ষেত্রে থাকে না। শারীরিক স্বাধীনতার ঘাটতি তার মানসিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা ও সৃজনশীল প্রতিভাকে মুক্তভাবে গড়ে উঠতে দেয় না। সাজ-পোশাকের এই চক্কর মেয়েদের বেশিরভাগ আগ্রহ ও পছন্দকে একটি ক্ষুদ্র গন্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলে। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সব মেয়েদের জন্যেই ‘ভাল বিয়ে’ হওয়া পরিবারের জন্য সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব সামাজিক মানদণ্ডে ‘সুন্দর’ হওয়ার বা থাকার জন্য চেষ্টা চালানো এবং এর জন্য সময় দেওয়া থেকে বিরত থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিয়ের পরেও স্বামীর সঙ্গে ‘সুসম্পর্ক’ ধরে রাখতে শরীরের সৌন্দর্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী নারীও সন্তানের কারণে, সামাজিক কারণে বিয়ে টিকিয়ে রাখতে চায়। আর বেশিরভাগ বিবাহিত নারীই অর্থনৈতিকভাবে স্বামীর উপর নির্ভরশীল। অতএব, শারীরিক সৌন্দর্যের চক্কর বৃদ্ধ হবার আগে নারীকে ছাড়ে না। এর প্রভাবে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতা খর্ব হয় এবং সৃজনশীল সম্ভবনার অনেক পথ বন্ধ হয়ে যায়।
সৌন্দর্যের চক্করের গভীরে যে সত্য রয়েছে তা হল- নারীর জীবন পুরুষকেন্দ্রিক এবং পুরুষের নিমিত্তেই তার অস্তিত্ব এবং সে তার ভোগের ও সাজিয়ে রাখার বস্তু। অতএব পুরুষের মনোরঞ্জনের অনুকূলে তার দেহকে পরিবর্তন করে ‘তৈরি’ করতে হবে তা যত কষ্টেরই হোক। কখনও বল প্রয়োগে তাকে তা করতে বাধ্য করা হয়, কখনও পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক প্রণোদনা থেকে সে নিজেই এতে নিয়োজিত হয়। এই বাস্তবতা নারীর মনের গভীরে নিজের এক অধীন, আবদ্ধ ও দেহ-সর্বস্ব প্রতিচ্ছবি তৈরি করে যা তার মনের মুক্ত বিকাশের বড় প্রতিবন্ধক। এই চক্কর নারীকে শরীর ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ থেকে বঞ্চিত করে এবং বেশিরভাগ নারীকে দুর্বল-চিত্ত, ভীরু, আত্মকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করে।
‘পর্দা’ কেবল ড্রেস-কোড বা শরীর ঢাকার বিষয় নয়। পোশাক ছাড়াও পর্দার আরও গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক রয়েছে। একটি হল নারীকে পারিবারিক চৌহদ্দি বা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থাকতে বাধ্য করা। অন্যটি হল পাবলিক প্লেসেও নারীদের পুরুষের থেকে আলাদা রাখা।
পৃথিবীর ব্যাপক অধিকাংশ সমাজে পুরুষতন্ত্রের উপস্থিতি থাকলেও অনেক সমাজেই এখন আর কঠোর অবরোধ প্রথা নেই। এই প্রথাকে, বৈধ অধিকর্তা ছাড়া অন্য সকল পুরুষের ‘ভোগ বা ভোগের লালসা’ থেকে নারীর শরীরকে ‘রক্ষা’ করার ‘প্রয়োজনীয়’ ও ‘কার্যকর’ প্রথা বলে দাবী করা হয়। ‘পর্দা’ কেবল ড্রেস-কোড বা শরীর ঢাকার বিষয় নয়। পোশাক ছাড়াও পর্দার আরও গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক রয়েছে। একটি হল নারীকে পারিবারিক চৌহদ্দি বা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থাকতে বাধ্য করা। অন্যটি হল পাবলিক প্লেসেও নারীদের পুরুষের থেকে আলাদা রাখা। অর্থাৎ ড্রেসকোড মেনেও গন্ডির বাইরে যাওয়া কিংবা ‘পর-পুরুষ’ বা অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে মেশা বা কথা বলা, পুরুষ সঙ্গী ছাড়া একা একা কোথাও যাওয়া ইত্যাদিরও অনুমোদন নাই এই প্রথায়। এই প্রথা যতটা না ধর্মীয় তার চেয়ে অনেক বেশি সাংস্কৃতিক ও পুরুষতান্ত্রিক। এর সঙ্গে জড়িত পুরুষতান্ত্রিক অহম এবং পারিবারিক ‘সম্মান’। তাই এই প্রথার প্রচলনের ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক পরিবার অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম। পর্দা খেলাপ করে ‘ইসলাম-বিরোধী’ জীবন যাপনের জন্য পারিবারিক সদস্য কর্তৃক বা অন্যান্যদের দ্বারা নারীদের নিহত বা গুরুতরভাবে আহত হবার ঘটনা অনেক ইসলামি দেশে প্রায়ই ঘটে থাকে। যে সব সমাজে এই প্রথা প্রচলিত আছে সেখানে পুরুষতান্ত্রিক অন্যান্য বিধিনিষেধের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এই প্রথাকে ব্যবহার করা হয়। পর্দার সীমানা কেবল চলাফেরা ও মেলামেশার বাধ্যবাধকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় মেয়েদের বিয়ে, শিক্ষা ও পেশাগত জীবনও পর্দার ‘রীতি’ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মেয়েরা কতদূর পড়তে পারবে, কী বিষয়ে পড়তে পারবে এবং পেশায় যেতে পারবে কিনা, গেলেও কোন পেশায় যেতে পারবে সে সিদ্ধান্ত পরিবার নেয় ‘পর্দার নীতি অনুযায়ী’। নারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অবরুদ্ধ করে রাখার এই প্রথা এবং তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজ ও পরিবারের কঠোর ও নির্মম অবস্থান নারীর মানসের উপর বহুমাত্রিক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
অবরোধ প্রথা এককভাবে ইসলাম ধর্মের ব্যাপার নয় কারণ অন্য ধর্মাবলম্বী নারীদের উপরও পোশাক-আবরণ এবং চলাফেরা ও অবস্থানের বিধি-নিষেধ রয়েছে। তবে ইসলাম ধর্মে এই প্রথা সবচেয়ে সংগঠিত ও কঠোর। অন্য ধর্মে এটা কেবল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচারের বিষয় কিন্তু ইসলামে এটা অনেকটা শাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত। মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে আমরা দেখি- যে সমাজ যত বেশি পশ্চাৎপদ বা যে সমাজে নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ যত বেশি সে সমাজে পর্দার বিধান তত কঠোর ও নির্মম। রোকেয়ার কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ অবরোধবাসিনী-তে অবরোধের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে তাতে আমরা দেখি অবরোধের মধ্যে থাকা নারীরা মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও মুখ খুলতে বা নড়াচড়ার সংকোচ কাটাতে পারছে না। কঠোর শৃঙ্খল ও অবদমনের মধ্যে থাকা নারী যে মানসিকভাবে কতটা শক্তিহীন হয়ে যায় এগুলো তারই নিদর্শন। স্বাভাবিক অনেক কাজ করার মানসিক শক্তি এবং নিজের পরিচিত চৌহদ্দির বাইরে সাবলীলভাবে চলাফেরা ও কাজকর্ম করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তারা। বাইরের জগত এবং পরিবারের বাইরে সমাজের অন্যসব বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এসব নারী একরকম ‘শিশুর মত অন্তকরণহীন’ হয়েই গড়ে উঠত। তাদের মন এতটাই আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে গড়ে উঠত যে পূর্ণবয়স্ক হয়েও তারা বিশ্বাস করত নিজেদের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা তাদের নেই।
আধুনিক জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বোধ থেকে আমরা উপলব্ধি করি প্রকৃতিগতভাবে নারী ও পুরুষের মানসিকতার বড় ধরণের পার্থক্য নেই। নারী পুরুষের মানসের যে পার্থক্য আমরা বিভিন্ন মাত্রায় দেখতে পাই তার প্রধান ও নির্ণায়ক কারণ হল তাদের ভিন্ন সামাজিক বাস্তবতা।
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার ও স্বাধীনতার অভাব নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইসলামি বিপ্লবের পর কঠোর অবরোধ ইরানের নারীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ইরানে আত্মহত্যার হার বৈশ্বিক গড়ের পাঁচগুণ এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে এর শতকরা ৮৩ জন হল নারী। কঠোর অবরোধ প্রথা চালু রয়েছে এমন অন্যান্য দেশেও নারীদের মধ্যে মানসিক রোগের প্রকোপ অবরোধমুক্ত দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। একদিকে ছেলেবেলা থেকে কঠোরভাবে আদ্যোপান্ত শরীর ঢাকার বাধ্যবাধকতা এবং অন্যদিকে চলাফেরা ও কর্মকান্ডের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ নারীর মনে বর্হিজগত সম্পর্কে গভীর সংবেদনশীলতা, ভীতি ও অদ্ভুত এক ধরণের ট্যাবু তৈরি করে ফলে অধিকাংশ মেয়েদের বহির্জগত সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা গড়ে উঠতে পারে না এবং তাদের সামাজিকীকরণও ব্যহত হয়। এভাবে বেড়ে ওঠা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বড় ধরণের ঘাটতি থাকে। পূর্ণবয়স্ক হলেও তারা আর নিজের দায়িত্ব নিতে সক্ষম হয়ে ওঠে না।
জন্মগতভাবে বনের পাখির মতই মুক্ত থাকে নারীর মন, এরপর পুরুষতান্ত্রিক খাঁচায় বন্দী থেকে তার পরিণতি হয় সেই খাঁচার পাখির মতই ভীরু ও নতজানু মানসিকতার। যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর মনস্তত্ত্বের এই রূপান্তর ঘটে তাকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে।
আধুনিক জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বোধ থেকে আমরা উপলব্ধি করি প্রকৃতিগতভাবে নারী ও পুরুষের মানসিকতার বড় ধরণের পার্থক্য নেই। নারী পুরুষের মানসের যে পার্থক্য আমরা বিভিন্ন মাত্রায় দেখতে পাই তার প্রধান ও নির্ণায়ক কারণ হল তাদের ভিন্ন সামাজিক বাস্তবতা। নারীপুরুষ কেউই লিঙ্গ নির্দিষ্ট মনোভাব ও আচরণ নিয়ে জন্মায় না। জন্মের পর সমাজ ও সভ্যতার প্রভাবই তাদের মধ্যে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট মানসিকতার জন্ম দেয়। এই ক্ষেত্রে জৈবিক পার্থক্যের চেয়ে সামাজিক মাত্রা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নারীর মধ্যে যে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট মানসিকতা আমরা দেখতে পাই এর বেশিরভাগ অংশ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জৈবিক পার্থক্যের কোনো ভূমিকা নেই। ঐতিহাসিকভাবে সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থা, বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক অবস্থানে থাকা এবং পুরুষের ভোগের বস্তু হিসেবে যে শরীরী চক্করে তাকে পড়তে হয় এই সবগুলি ব্যাপারই মূলত এ সমাজে নারীর মধ্যে ‘নারীসুলভ’ মানসিকতার জন্ম দেয়। জন্মগতভাবে বনের পাখির মতই মুক্ত থাকে নারীর মন, এরপর পুরুষতান্ত্রিক খাঁচায় বন্দী থেকে তার পরিণতি হয় সেই খাঁচার পাখির মতই ভীরু ও নতজানু মানসিকতার। যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর মনস্তত্ত্বের এই রূপান্তর ঘটে তাকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে। তাহলেই আমরা এর সঠিক রূপ এবং ভেতরের বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারব এবং এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার পথও আমাদের সামনে উন্মুক্ত হবে।
মনিরুল ইসলাম: বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, লেখক ও শিক্ষক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ।
ইমেইল: monirul852@gmail.com
তথ্যসূত্র:
১১০। Manon Garcia :We Are Not Born Submissive: How Patriarchy Shapes Women’s Lives, Published in English Language in 2021,by Princeton University Press, Originally published as On ne naît pas soumise, on le deviant, pp-204.
১১১। Simone De Beauvoir : The Second Sex; Translated and Edited By H. M. Parshley, Jonathan Cape Thirty Bedford Square, London, 1956, pp-567